ছেলেবেলার ঈদ
ছেলেবেলায় আমি ছিলাম খুবই দুরন্ত ও বোকা

আমার তরুণ ছাত্রদের মাঝে মধ্যে আমি একটা গল্প শোনাই। বলি ধর, মাকে নানাভাবে জপিয়ে তার কাছ থেকে তুমি একশ টাকা হাতিয়ে নিলে। ধর, সেই টাকা নিয়ে তুমি রেস্টুরেন্টে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ফুর্তি করে খেয়েদেয়ে তা ওড়ালে। এই খাওয়া-দাওয়ায় নিশ্চয়ই একটা আনন্দ আছে, তা তুমি পেলে; কিন্তু ধর বাড়ি থেকে বেরোতেই যদি অন্য কিছু ঘটত; ধর রাস্তায় পা বাড়াতেই তুমি দেখতে পেলে একটা অসুস্থ মুমূর্ষু না-খাওয়া লোক তোমার সামনেই অচেতন হয়ে পড়ে গেল। তাকে দেখে তোমার ভেতর তখন যদি মমতা এসে যেত; একজন অনাহারি নির্জীব আর মৃত্যুপথযাত্রী লোককে সামনে ফেলে রেস্টুরেন্টে গিয়ে বন্ধুদের নিয়ে ফুর্তি করতে নিজেকে অপরাধী মনে হতো। ধর তুমি যদি পকেটের সেই টাকা খরচ করে তাকে গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে, সে ভালো হয়ে উঠলে তাকে খাবার কিনে দিয়ে ঘরে যাবার ব্যবস্থা করে বাড়ি ফিরতে- তাহলে টাকাটার আর একটা ব্যবহার হতো। নিশ্চয়ই মানবে: রেস্টুরেন্টে ফুর্তি করে টাকা ওড়ানোর মতোই ওই টাকাগুলোকে একজন দুঃখীর কষ্ট দূর করার জন্য দিয়ে দেবার মধ্যেও একটা আনন্দ আছে। এখন প্রশ্ন, এই দুই আনন্দের মধ্যে বড় কোনটি? নিশ্চয়ই দ্বিতীয়টি। একটা ভোগের মত্ততায় স্কুল, অন্যটা দেবার তৃপ্তিতে পবিত্র। জীবনের সূচনার দিনগুলোয় এই পবিত্র আনন্দের সঙ্গে জানাজানি না হলে এ তো আমাদের কাছে অপরিচিত থেকে যাবে।
ছেলেবেলায় হিন্দি ভাষার একটা ইসলামি গান শুনতাম:
‘মিলতা হ্যায় কেয়া নামাজ মে
সেজদা মে যাকে দেখলে।’
শৈশবের কচি, অনুভূতিময় ও নিষ্পাপ দিনগুলোয় যে মানুষ এই সেজদাকে চিনল না, তার জীবনে তো ওই উচ্চতর আনন্দের সূচনাই হলো না। সে কী করে জীবন-নামাজের মমার্থ বুঝবে?
ছেলেবেলায় আমি ছিলাম খুবই দুরন্ত। দুরন্ত কিন্তু সরল সোজা। ধ্বংসাত্মক বা ক্ষতিকর প্রবণতা আমার মধ্যে প্রায় ছিলই না। আজও নেই। আমার ছেলেবেলা ভরা ছিল অফুরন্ত খেলাধুলায়, গাছে গাছে ঘুরে বেড়ানোর দুরন্ত আনন্দে, সাঁতারে আর দূর-দূরান্তে হারিয়ে যাওয়ার উপচানো খুশিতে। আমার ছোট ভাই মামুনও ছিল অসম্ভব দুরন্ত; কিন্তু ওর দুরন্তপনার মধ্যে প্রায়ই একটা ধ্বংসাত্মক অভিসন্ধি কাজ করত। ও প্রায়ই ওর অশুভ তৎপরতাগুলোর সঙ্গে সুকৌশলে আমাকে জড়িয়ে নিত; কিন্তু বিপদ দেখলেই আমাকে সামনে এগিয়ে ‘দিয়ে নিঃশব্দে পেছন থেকে সরে পড়ত। ফলে গল্পের বাজিকরের সেই বোকা ছাগলের মতো যাবতীয় শাস্তি আমাকে পিঠ পেতে নিতে হতো। মারধর খেতে হতো প্রায়ই। ব্যাপারটা কেমন তা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই। এক দিন মামুন আমাকে খবর দিল, রান্না ঘরে মিটসেফের ওপরের তাকে এক হাঁড়ি দুধ জাল দিয়ে ঘন করে রাখা হয়েছে। তাতে আছে বেজায় পুরু সর।
আমি বোকা-সরল মানুষ। বললাম, ‘সর পড়েছে তো কী হয়েছে?’ মামুন বলল, ‘চলেন হাঁড়িটা নামিয়ে আমরা খেয়ে ফেলি।’ দুধটা সবার জন্য জাল দিয়ে রাখা হয়েছে, তাই শুধু দুজনে কেন আমরা খাব, ভাবনাটা প্রথমে আমার মাথাতেই আসেনি। ওর কথা শুনে ব্যাপারটা মাথায় এলো, ‘তাই তো, হাঁড়ি নামিয়ে তো সবটা সর দুজনে খেয়ে নেয়া যায়!’
বললাম, ‘চল।’
মা ঘুমিয়ে ছিলেন শোবার ঘরে। আমরা পা টিপে টিপে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম।
মিটসেফ বেশ বড়। ওপরের তাকটা আমার মাথার চেয়েও ফুটখানেক উঁচুতে। সেই তাকে হাঁড়ি। কাজেই মিটসেফ বেয়ে ওপরে উঠতে না-পারলে হাঁড়ি নামানো সম্ভব নয়। আমি মিটসেফের তাক বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। মামুন পেছন থেকে দুহাতে ঠেলে আমাকে উঠতে সাহায্য করে চলল; কিন্তু আগেই বলেছি আমি ছিলাম বেজায় মোটাসোটা। আমার ভার মিটসেফ সহ্য করতে পারল না, বিরাট শব্দে আমার ওপরে পড়ে গেল। মিটসেফের ভার ঘাড়ে নিয়ে হাঁড়ির দুধের মধ্যে আমি গড়াগড়ি যেতে লাগলাম। বিকট শব্দে মিটসেফ পড়া আর সেই সঙ্গে আমার তীব্র চিৎকার- এই দুয়ে মার ঘুম ভেঙে গেল। তার ধারণা হলো আমার বিপজ্জনক কিছু হয়েছে। উনি হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলেন রান্নাঘরের দিকে। মামুন প্রথমে চেষ্টা করছিল আমাকে মিটসেফের নিচ থেকে বের করতে; কিন্তু মা রান্নাঘরে ঢুকছেন টের পেতেই ও আস্তে করে দরোজার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল আর মা ঘরে ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পেছন দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।
মা ভেবেছিলেন মিটসেফের নিচে পড়ে আমি হয়তো থেঁতলে গেছি; কিন্তু মিটসেফ সরিয়ে যখন দেখলেন যে আমি পুরোপুরি সুস্থ এবং হৃষ্টপুষ্ট তখন দুর্ঘটনায় আমার যতটুকু আহত হবার কথা ছিল, তা তিনি নিজের হাতে সম্পূর্ণ করে দিলেন।
এই সুযোগে আমার জীবনের একেবারে প্রথম শিক্ষকের গল্পটি এখানে বলে নিই। গল্পটি শুনলে মামুনের উপস্থিত বুদ্ধি আর তোড়িয়া মেজাজের আরও কিছুটা প্রমাণ মিলবে। গল্পটা যেমন মজার তেমনি কষ্টের।
আমাদের সেই স্যারের নাম আজ পুরোপুরিই ভুলে গেছি; কিন্তু নাম মনে না থাকলেও তার চেহারা এখনো ভয়ার্ত-রেখায় আমার মনের ক্যানভাসে আঁকা হয়ে আছে। অসম্ভব পেটাতেন তিনি আমাদের। পেটাতেন না বলে বলা যায় চাবকাতেন। স্যার ছিলেন রোগা লিকলিকে একহারা চেহারার মানুষ। তার মুখ ছিল লম্বা, ছুঁচালো। তার কথা মনে হলে এখনো আমার মনে ছেলেবেলার গল্পে পড়া-শেয়াল পণ্ডিতের লোভী-চতুর এবং ধূর্ত মুখটা থেকে থেকে ভেসে ওঠে। স্যারের চোখ দুটি ছিল রুক্ষ আর কঠিন। কান দুটি লোমে ভর্তি। ছেলেবেলায় শুনতাম, কানে লোমওয়ালা লোকদের রাগ বেশি হয়। বড় হয়ে আমার কানেও লোম হয়েছে; কিন্তু আজও তো আমার ভেতর রাগের তেমন কোনো আলামত দেখছি না!
স্যারের রাগ সত্যি ছিল ভয়ংকর। লম্বা লিকলিকে বেত দিয়ে অসুস্থের মতোন পেটাতেন তিনি আমাদের। পেটাতে পেটাতে তার মুখ রক্তাভ আর হিংস্র হয়ে উঠত, তার বেতের নির্মমতায় আমাদের কিশোর-বয়স ফালিফালি হয়ে যেত। সেই ক্ষত আমাদের চামড়া কেটে নির্মম তীক্ষ্ণ হিংস্র রেখায় বসে যেত শরীরের ওপর। প্রায় প্রতিদিনই স্যার এভাবে পেটাতেন আমাদের।
প্রতিদিন এসেই স্যার প্রথমে আমাকে পড়া ধরতেন। সামান্য ভুল হলেই শুরু হতো তার চাবকানি। তার তীক্ষ্ণ বেত্রাঘাতের সঙ্গে সংগতি রেখে শরীর বাঁকিয়ে চুরিয়ে শুরু হতো আমার নানারকম কসরৎপূর্ণ উচ্চাঙ্গ ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্য। শপাং শপাং বেতের মুখে চলতে থাকত আমার কখনো ভরতনাট্যম, কখনো কত্থক, কখনো মণিপুরি হয়ে ওড়িশির অলৌকিক প্রদর্শনী। আমার পর্ব শেষ হলে শুরু হতো মামুনের পর্ব। এমনি করেই দিন যেত।
আগেই বলেছি মামুন ছিল তেড়িয়া আর ওর প্রতিভা ছিল নব নব উন্মেষশালিনী। এক দিন হঠাৎ করেই ও তার একটা প্রমাণ দিল। সেদিন স্যার এসেছিলেন সময় মতোই। প্রথমে নিয়মমতো শুরু হয়েছে আমার নাচ। বেশ অনেকক্ষণ ধরেই চলেছে সেটা। এরপর মামুনের পালা। প্রতিদিনের মতো দেখলাম স্যার বেতিয়ে চলেছেন আর মামুন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বিকৃত আর্তনাদে প্রতিদিনের নৃত্য পরিবেশন করে চলেছে। হঠাৎ করেই কী যেন একটা ব্যাপার ঘটে গেল। দৃশ্যপট পাল্টে গেল মুহূর্তে। দেখি, মামুন নয়, উল্টো স্যারই নাচছেন। হ্যাঁ, স্বয়ং স্যার। আমাদের প্রতিদিনকার মুদ্রাতেই আমাদের মতো করেই নাচছেন তিনি। সাদা ধুতির ভেতর থেকে সরু সরু লম্বা কালো পায়ের পাতাদুটি মাটিতে ঠুকে শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে নৃত্যের বিচিত্র কারুকার্য সৃষ্টি করে নাচছেন। মুহূর্তেই ব্যাপারটা বোঝা গেল। মার খেতে-খেতে অসহ্য মামুন এক সময় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে স্যারের বেত কেড়ে নিয়ে ক্ষিপ্তের মতো স্যারের দু-পা লক্ষ করে চাবকাতে শুরু করেছে।
সেই ঘটনার পর স্যারকে আমাদের বাসায় আর দেখিনি। হয় তিনি নিজেই চলে গিয়েছিলেন, নয় তাকে বিদায় দেয়া হয়েছিল। এত শক্তিশালী একটা স্বৈরাচারী যুগের অবসান যে এত সহজে হবে, সেটা আমরা ভাবতে পারিনি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনে একের পর এক স্বৈরাচারী শাসকদের অমনি নির্বোধ পতন দেখে বুঝতে পেরেছিলাম সব স্বৈরাচারী শাসকই হয়তো শেষ বিচারে স্যারেরই মতো। অমনি কাগুজে বাঘ। এদের বাইরের ভয়ংকর চেহারার আড়ালে ভেতরটা একেবারেই ফাঁপা আর শেকড়হীন। স্যারের কথা মনে হলে ধুতির ভেতর থেকে বেরিয়ে-আসা কালো কাঠি কাঠি পা-দুটির নৃত্যরত অসহায় ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।
ক্লাস সেভেন ও এইটে আমার চোখে যে সবচেয়ে বেশি বিস্ময় জাগিয়েছিল সে মাহবুব আলম। ক্লাস সেভেনে ওঠার পর হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের দুই সেকশনে ভাগ করে দেয়া হয়। হিন্দু ছাত্রদের দেয়া হয় এ-সেকশনে, মুসলমান ছাত্রদের বি-সেকশনে। ফলে আমি বি-সেকশনে চলে যাই। সম্ভবত এই সময় মাহবুব আলম আমাদের সেকশনে এসে ভর্তি হয়। সেভেন থেকে টেন পর্যন্ত ও ছিল আমাদের ফার্স্ট বয়। মাহবুব আলমের হাতের লেখা ছিল মুক্তার মতো। ওর পরীক্ষার খাতাগুলোকে লাগত শিল্পীর আঁকা ছবির মতো, পরীক্ষকের পক্ষে সেখানে কলম ছোঁয়ানোর উপায় ছিল না। পরীক্ষায় ও যা নম্বর পেত, তা বয়ে নিতে ওর আলাদা ঝুড়ির দরকার হতো। স্যাররা সবাই ওকে আদর করতেন। ওর জন্য গর্ববোধ করতেন। একবার উর্দুর হুজুর নাকি ওর খাতা পড়ে এমনই খুশি হয়েছিলেন যে, একশর মধ্যে একশ দশ দিয়ে ফেলেছিলেন (ভুলটা হয়েছিল মাহবুব আলমের একটা দুষ্টুমির কারণে। দুষ্টু মাহবুব উত্তর দেবার সময় যে ‘অথবা’সহ তিনটি বেশি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বসে আছে, তা তিনি ধরতে পারেননি। খাতা দেখার পর নম্বর যোগ দিতে গিয়ে ব্যাপারটা তার চোখে পড়ে)। মেধায়, দীপ্তিতে, প্রখরতায় ও ছিল ক্লাসের সবার থেকে জ্বলজ্বলে।
এক দিন ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। আমরা সবাই ক্লাস করছি, হঠাৎ এক কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক, পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি, মচমচ করে ক্লাসে ঢুকেই স্যারকে জিজ্ঞেস করলেন: ‘মাহবুব আলম কি আছে ক্লাসে?’
চেয়ারে বসে ক্লাস নিচ্ছিলেন নিত্যানন্দ বাবু। মাহবুব আলমের নাম শুনতেই স্যার প্রায় হাইজাম্পের ভঙ্গিতে চেয়ার থেকে মেঝেতে লাফিয়ে পড়ে স্ফারিত দৃষ্টিতে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন: ‘কে আপনি?’
যেন অন্য কোনো নক্ষত্র থেকে তিনি এসেছেন।
ভদ্রলোক নম্রভাবে বললেন: ‘আমি মাহবুব আলমের বাবা!’
উত্তর শুনে স্যার আনন্দে গর্বে পাগলের মতো হয়ে গেলেন। বারে বারে বলতে লাগলেন: ‘আপনি মাহবুব আলমের বাবা। আমাদের মাহবুব আলমের বাবা আপনি? ও তো রত্ন। আমাদের গৌরব! ও-ই তো স্কুলের মুখোজ্জ্বল করবে!’ বলে এমনভাবে মাহবুব আলমের বাবাকে সম্মানে সংবর্ধনায় আপ্লুত করতে লাগলেন যে, আমরা আমাদের হতভাগ্য বাবাদের নিয়ে যে কোথায় লুকোব বুঝে উঠতে পারলাম না।
ভালো ছাত্রদের নিয়ে আমাদের শিক্ষকদের কী স্নেহ আর গৌরববোধই না দেখেছি সে সময়ে!
আমরা ভেবেছিলাম মাহবুব আলম বাস্তবজীবনে অসাধারণ সাফল্য দেখাবে; কিন্তু তা হয়নি। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় একটা মোটামুটি ফার্স্ট ডিভিশন পেলেও পরের পরীক্ষাগুলোতে ফলাফল ছিল আরও সাদামাটা। যে ছিল স্কুলের ‘রত্ন’, ‘গৌরব’- সে একটা গড়পরতা চাকরি করে সাধারণ চাওয়া-পাওয়ার ভেতর জীবন শেষ করেছে। আমি একেক সময় ভেবেছি কেন হয় এমনটি। ওই বয়সে যারা থাকে সেরা ছাত্র-সারা স্কুলের ‘জ্যোতিষ্ক’ বা ‘বিস্ময়’-কেন তাদের অনেকেই একসময় উল্কার মতো ঝরে মরে ছাই হয়ে যায়। কেবল মাহবুব আলমের ব্যাপারে নয়, শিক্ষকজীবনজুড়েই আমি দেখেছি ব্যাপারটা।
লেখক: শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারক।


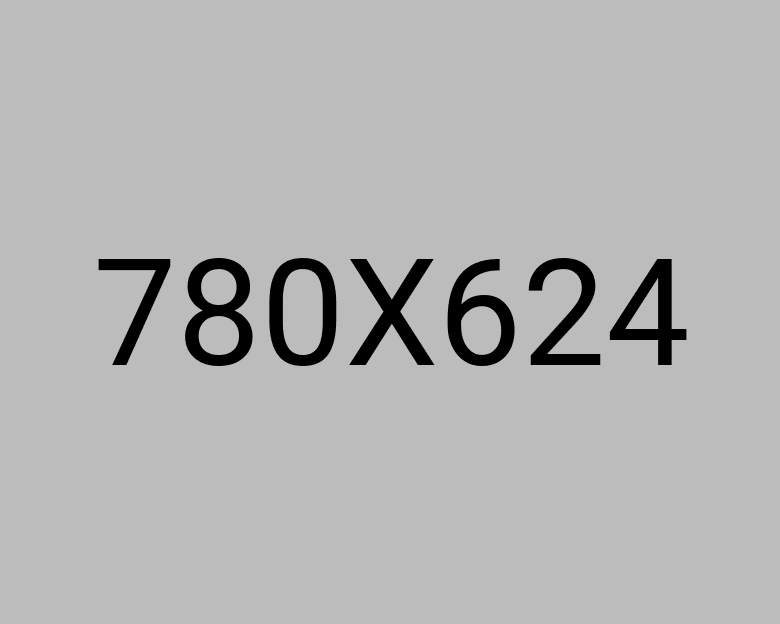
মতামত দিন
মন্তব্য করতে প্রথমে আপনাকে লগইন করতে হবে