লোকাল ব্র্যান্ডের পণ্য কি হারিয়ে যাচ্ছে?

সত্তর, আশি ও নব্বই দশক আর একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থায় একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করেছিল বেশ কিছু জনপ্রিয় পণ্য। দেশের মানুষের চাহিদা মিটিয়ে ওইসব পণ্য বিদেশেও রপ্তানি করা হতো। কালের বিবর্তনে ওই সময়ের বেশিরভাগ পণ্যই এখন বাজারে খুব একটা দেখা যায় না। তবে একটু স্মৃতিকাতর হলেই মানসপটে ভেসে ওঠে সেসব পণ্য। সাদাকালো যুগের টেলিভিশন, এমনকি নব্বই দশকে রঙিন টেলিভিশনের পর্দায় জনপ্রিয় পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখা যেত, যা সাধারণ মানুষের মনে প্রশান্তিও জাগাত।
আমরা যারা নব্বই দশকে বেড়ে উঠেছি, তাদের স্মৃতির মানসপটে এখনো দোলা দেয় জনপ্রিয় মিমি চকলেট, নাবিস্কো গ্লুকোজ বিস্কুট, নাবিস্কো লজেন্স, দেশের প্রথম বলপয়েন্ট কলম ইকোনো, বলাকা রেজার, হকের ৭৮৬ ব্যাটারি, প্রজাপতি ম্যাচ, লালবাগ কেমিক্যালের হাসমার্কা গন্ধরাজ সুগন্ধী কেশতেল, রানী মার্কা ঢেউটিন, কমান্ডার সোপ কোম্পানির কসকো গ্লিসারিন সাবান, মিল্লাত ঘামাচি পাউডার, তিব্বত স্নো, জেট গুঁড়ো সাবান। এমন কী হাল আমলের অনিক মোবাইলের ব্যাটারিসহ কত শত পণ্য। কয়েক দশক ধরে এসব পণ্য দেশের বাজারে সফলতার সঙ্গে ব্যবসা করেছে।
জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের পণ্যগুলো বাংলার ঘরে ঘরে প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি বিদেশের মাটিতেও দাপিয়ে বেড়িয়েছে, শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে দেশের অর্থনীতিকে। তবে এখন কেন ওই পণ্যগুলো বাজারে খুব একটা দেখা যায় না? পরিসংখ্যান বলছে- এক সময়ের জনপ্রিয় এই পণ্যের বেশিরভাগই বর্তমানে তৈরি হয় না। অনেক প্রতিষ্ঠান একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, কোনটা বিক্রি হয়ে গেছে, আবার কোনটা ধুকে ধুকে চলছে। বাজারে আগের সেই প্রডাক্টগুলোর দুই-একটি পাওয়া গেলেও, মান আগের মতো নেই; চাহিদাও তলানিতে চলে গেছে সময়ের প্রয়োজনে।
সত্তর, আশি ও নব্বই দশক কিংবা একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জনপ্রিয় পণ্যগুলোর মান যে খারাপ ছিল, তা কিন্তু নয়। মান নিয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না। তবে নানাবিধ কারণে ওইসব পণ্যের চাহিদা ও উৎপাদন কমে যাওয়ায় আমাদের আমদানিনির্ভরতা বেড়েছে। যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে বেশ কিছু কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক সময় কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি ও বিদেশ থেকে পণ্য আমদানিতে দীর্ঘ সময় এবং নানা জটিলতায় পড়ে পণ্যের উৎপাদন কমে গেছে। আবার মার্কেটিং পলিসি এবং সরবরাহ সিস্টেম টেকসই না হওয়ায়, পণ্যের বাজারজাত ব্যবস্থা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলোর সঠিক বিতরণ ব্যবস্থা না থাকায়। ‘মার্কেটিং পলিসি’ ও ‘ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম’ বাস্তবতার নিরিখে না হওয়ায়, অনেক লাভজনক প্রতিষ্ঠান চোখের সামনে মুখথুবড়ে পড়েছে, কোনটা আবার একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। যদিও বর্তমানে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ধুকে ধুকে চলছে তবে সেটাকে ঠিক ‘চলা’ বলে না। কসকো সাবান এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ দীর্ঘ কয়েক দশক মানুষের কাছে জনপ্রিয় ছিল দেশের প্রথম গ্লিসারিন সমৃদ্ধ কসকো সাবান। হোটেল, রেস্তোরাঁ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অফিস ও বাসা-বাড়িতে মানুষ প্রতিদিন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করতো কম ক্ষয় হওয়া এই সাবান। আর বিয়ে, জন্মদিনসহ বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কসকো সাবান ব্যবহারের বিকল্প ছিল না বহু বছর।
এখন কি বাজারে খুব একটা দেখা মেলে এই সাবানের? আপনাদের অনেকের হয়তো খেয়াল আছে- একটা সময় দেশের মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারে সকাল-বিকাল নাস্তার জোগান হতো নাবিস্কোর গ্লুকোজ বিস্কুট দিয়ে। এমনকি বাসা-বাড়িতে মেহমান এলে তাদের আপ্যায়ন করা হতো ঐতিহ্যবাহী গ্লুকোজ বিস্কুট দিয়ে। বাঙালির মানসপটে চির স্মরণীয় হয়ে আছে এই বিস্কুটটি। তবে পরিতাপের বিষয় হলো- অনেক বছর ধরে মার্কেটে অসংখ্য নামি-দামি ও দেশি-বিদেশি বিস্কুটের ভিড়ে হারিয়ে গেছে এক সময় চরম দাপটের সঙ্গে ব্যবসা করা ব্র্যান্ড নাবিস্কো গ্লুকোজ বিস্কুট।
এই তো কিছু কাল আগ পর্যন্ত মা-খালা আর নানি-দাদিদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল লালবাগ কেমিক্যালের হাসমার্কা গন্ধরাজ সুগন্ধী কেশতেল। গন্ধরাজ নারিকেল তেল চুলে দিয়ে রোদ পোহায়নি বা ব্যবহার করেনি এমন নারী বাংলার তল্লাটে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কোথায় গেলো সেই গন্ধরাজ তেল? এখন বাজার হরেক রকম কোম্পানির নারিকেল তেলে সয়লাব। দোকানিকে গন্ধরাজের কথা জিজ্ঞেস করলে চোখ হয়তো কপালে তুলতে পারেন!
কেস স্টাডি :
একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশে সব বয়সী মানুষ চকলেট বলতে শুধু মিমিকেই বুঝতো। হ্যাঁ, বলছি মিমি চকলেটের কথা। পূর্ব পাকিস্তান আমলে বেসরকারি উদ্যোগে ১৯৬৫ সালে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় মিমি চকলেট কোম্পানি। দেশ স্বাধীনের পর এটির চাহিদা ও উৎপাদন ভীষণভাবে বাড়তে থাকে। ওই সময় বিদেশ থেকে আমদানি করা ‘কিটক্যাট’ এবং ‘মারস’ চকলেট ভীষণ দামি এবং বড় লোকের সন্তানদের দারুণ পছন্দের ছিল। এর বিপরীতে সাশ্রয়ী মূল্যে সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি হতো মিমি চকলেট। তাই ছোট-বড় সবার কাছে দারুণ জনপ্রিয় ছিল অরেঞ্জ ও মিল্ক এই দুই স্বাদের চকলেট। ২০০০ সাল পর্যন্ত বেশ দাপটের সঙ্গে ব্যবসা করেছে প্রতিষ্ঠানটি। তবে নব্বই দশকে বাজারে বেশ কটি নতুন চকলেট কোম্পানির আবির্ভাব ঘটায়, ধীরে ধীরে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে প্রতিষ্ঠানটি।
এক পর্যায়ে লোকসান বাড়তে থাকে। এ ছাড়া, পুরোনো মেশিন ব্যবহার করায় একটা সময় উৎপাদন খরচও বেড়ে যায়। যোগ্য ও প্রযুক্তি জ্ঞানসমৃদ্ধ দক্ষ নেতৃত্বের অভাব এবং ডিস্ট্রিবিউশন পলিসি জনবান্ধব না হওয়ায়, বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনি মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে থাকা প্রতিষ্ঠানটি। এর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও চরম আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি আর লুটপাটের অভিযোগ ওঠে। গ্রামের তুলনায় মিমি চকলেট শহরের দোকানগুলোতে বেশি পাওয়া যেতো। প্রতিষ্ঠানটির মার্কেটিং এবং ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্র্যাটেজি দুর্বল থাকায় গ্রামে-গঞ্জে চাহিদা ব্যাপক থাকলেও সরবরাহ কম ছিল। পরে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি কোম্পানিটি।
ফলে, এক প্রকার বাধ্য হয়ে সরকার ২০১৮ সালে মিমি চকলেট প্রতিষ্ঠানটিকে পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। এই যে অনেক নামি-দামি প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলো হারিয়ে গেলো এতে ক্ষতি কাদের হলো ? বাস্তবে ক্ষতি এ দেশের মানুষেরই হয়েছে। কারণ দেশে কয়েক দশক ধওে বিভিন্ন পণ্যের জন্য আমদানি নির্ভরতা বেড়েছে। বিদেশ থেকে আনা কাঁচামালের দাম বেশি হওয়ায় উৎপাদন খরচ বেশি হয়। সুতরাং সাধারণ মানুষকে বেশি দাম দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে হচ্ছে। দেশে মার্কেট বড় হলে অসংখ্য বেকার তরুণের কর্মসংস্থান হতো, অর্থনীতি চাঙ্গা হতো; যেই এলাকায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতো সেখানের অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত হতো।
করণীয় কী :
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত দেশবাসীকে সাশ্রয়ীমূল্যে পণ্য পৌঁছে দিতে কেন্দ্রীয় বিতরণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো দেশের কিছু বড় স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান। কোম্পানিগুলোর দেশব্যাপী ৬৪টি জেলায় কেন্দ্রীয় বিতরণ ব্যবস্থা রয়েছে। তারা নিজস্ব কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বা থার্ডপার্টি লজিস্টিকস সার্ভিসের সারা দেশে পণ্য পরিবহন করছে। যেসব প্রতিষ্ঠানের ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম দুর্বল এব পর্যাপ্ত জনবল নেই তারা এসব প্রতিষ্ঠানের মতো বৃহৎ ও শক্তিশালী প্রযুক্তিনির্ভর বিটুবি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিয়ে দেশব্যাপী পণ্য সরবরাহ করতে পারে।
সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম কি সাশ্রয়ী?
এলসি বা লেটার অব ক্রেডিট খুলতে বেশিরভাগ কোম্পানির প্রচুর অর্থ এবং সময়ের অপচয় হয়। তবে, সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম বা কেন্দ্রীয় বিতরণ ব্যবস্থা চালু হলে এটি আর হবে না। দেশের মানুষের চাহিদা মিটিয়ে পণ্য বিদেশে রপ্তানিও করা যাবে।
বর্তমান প্রেক্ষাপট:
আমাদের দেশে খাদ্য ও নিত্যপণের বিতরণ ব্যবস্থা পরিচালিত হয় ব্যবসায়ীদের নেতৃত্বে এক ধরনের সিস্টেমের মাধ্যমে, যেখানে স্বচ্ছতার বিষয়টি একেবারেই কম থাকে। বিভিন্ন ফরমাল ও ইনফরমাল প্লেয়াররা এই ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ছোট-বড় দোকানদার, দাদনদার, মহাজন ও পাইকারি ব্যবসায়ী প্রত্যেকেই এই সরবরাহ ব্যবস্থায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে রশি টেনে ধরে। এই ধরনের ব্যবস্থায় সব সময় পণ্যের দামে অস্থিরতা এবং সরবরাহে সময় অপচয় হয়। এর কারণ হলো- প্রত্যেক বিক্রেতা তার নিজের মতো দাম ঠিক করে এবং বেশি লাভ করতে পণ্যের প্রাপ্যতার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে। এ অবস্থায় শুধু পণ্যের দামই নয়, সিস্টেম লস রোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি অপচয়ের সঠিক তথ্য অনেক সময় পাওয়া যায় না। কারণ বিক্রেতারা ঐক্যবদ্ধভাবে সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা করে।
সমাধান কীভাবে হবে?
জরুরিভিত্তিতে আমাদের যেটি করা দরকার, সেটি হলো- উৎপাদকের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় বিতরণ ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পণ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ এবং সব উৎপাদককে নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করবে। এর অর্থ হলো বর্তমান ব্যবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে দামের যে ওঠানামা তা দূর করে স্থিতিশীলতা আনা যাবে। এতে ক্রেতারা দামের নৈরাজ্য থেকে মুক্তি পাবে এবং পণ্যের সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এ ধরনের একটি স্বচ্ছ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পদ্ধতিগত অদক্ষতা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব। এভাবে উদ্যোগ নিলে বর্তমানে যে পরিমাণে পণ্য নষ্ট হয়, তা মোটা দাগে কমে আসবে।
আমরা যখন দোকানি বা ব্যবসায়ীদের নেতৃত্বে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা মডেল থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে বিতরণ মডেলে যাবো, তখন আমাদের পণ্য সরবরাহের পাশাপাশি অন্যান্য দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। বর্তমানে ব্যবসায়ী, দাদনদার, মহাজন, পাইকারি বিক্রেতারা শুধু বিতরণ ব্যবস্থা নয়, বিভিন্ন অংশীদার যেমন : কৃষক, উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াকারী এবং বিক্রেতাকে নগদ অর্থ সরবরাহ করে। কেন্দ্রীয় বিতরণ ব্যবস্থা চালু হলে স্থানীয় পাইকারি ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত দাম হাতিয়ে নেওয়ার দিন শেষ হয়ে যাবে, এটিই মূলত কেন্দ্রীয় বিতরণ মডেলের সাফল্য। বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে উর্বর দেশগুলোর একটি। আমরা গত অর্থবছরে ৯ দশমিক ৩ মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদন করেছি। তারপরও দুঃখজনক বিষয় হলো আমরা বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ খাদ্য আমদানিকারক দেশ। এর পরিমাণ ১ দশমিক ২৫ কোটি মেট্রিক টন।
পরিশেষে:
নিত্যপণ্যের ক্ষেত্রে আমাদের আমদানিনির্ভরতা কমাতে সেন্ট্রাল ডিস্টিবিউশন সিস্টেম সহায়তা দেবে। যেহেতু আমাদের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, তাই স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত খাদ্য ও নিত্যপণ্যের সরবরাহ জোরদার করতে হবে। আর ভবিষ্যতে এটি অর্জনের জন্য একটি সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা খুবই জরুরি। এতে স্থানীয় সব উৎপাদক, প্রক্রিয়াকারী ও প্রস্তুতকারকরা সমানভাবে বাজারে ঢুকতে পারবে। তখন অল্প কিছু লোক আগের মতো আর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। এই উদ্যোগ শুধু আমাদের সম্ভাব্য সংকট থেকেই রক্ষা করবে না, আমাদের উর্বর ভূমির দক্ষতা ও কারখানার উৎপাদনে গতিশীলতা নিশ্চিতে সহায়ক হবে। একটি শক্তিশালী ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের উর্বর ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারি, যা থেকে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দারুণভাবে লাভবান হতে পারে।
বায়েজিদ আহমেদ: সাংবাদিক ও গবেষক।


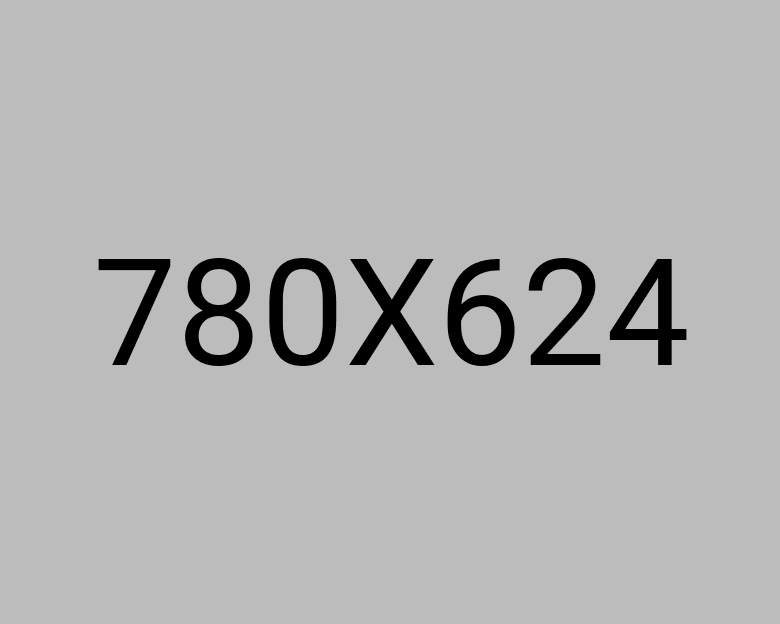
মতামত দিন
মন্তব্য করতে প্রথমে আপনাকে লগইন করতে হবে