বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক দর্শনে স্বাধীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির যে ভিত্তি বা ফাউন্ডেশন, তার প্রধান আর্কিটেক্ট হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা এবং একই বছর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন এবং ভারত হয়ে বাংলাদেশে আসেন। তার এই প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই তিনি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পররাষ্ট্রনীতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। পরে দেশে এসে তিনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যে ভাষণ দেন, সেখানেও ভবিষ্যৎ পররাষ্ট্রনীতির ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু তার বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে দুটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। এগুলোই ছিল বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলভিত্তি বা ফাউন্ডেশন। বর্তমান সরকারও বঙ্গবন্ধু অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন করে চলেছেন। বঙ্গবন্ধু একাধিকবার বলেছেন, বাংলাদেশ হবে প্রচ্যের সুইজারল্যান্ড। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু বলতেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল কাঠামোই হবে, ‘সবার প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি শত্রুতা নয়। সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলভিত্তি তৈরি করে গেছেন।
বঙ্গবন্ধু শুধু মুখেই এ কথা বলেননি। তিনি তার পররাষ্ট্রনীতিকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫নং ধারায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির স্বরূপ বা বৈদেশিক সম্পর্কে ভিত্তি কী হবে, তার একটি ধারণা দেয়া হয়েছে। সেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যেসব মৌল নীতি অনুসরণ করা হবে, তা হলো জোট নিরপেক্ষতা, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। যে সব দেশ বা জনগোষ্ঠী নির্যাতিত হচ্ছে, তাদের সমর্থন দেয়া। ১৯৭১-১৯৭২ সালের বাস্তবতায় বিশ্বব্যাপী বর্ণবাদ একটি বড় মানবিক সমস্যা ছিল। বিশ্বব্যাপী বর্ণবাদের বিরোধিতা করাও বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির একটি বড় ধরনের অঙ্গীকার ছিল। এ ছাড়া কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা অর্থাৎ প্রত্যেকটি দেশের স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল।
পররাষ্ট্রনীতির এই বিষয়গুলো শুধু মুখে বলা হয়নি। আমাদের রাষ্ট্রীয় সংবিধানেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ’৭০-এর দশকে জোট নিরপেক্ষতা আন্তর্জাতিকভাবেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভবিষ্যৎ গতিপথ কেমন হবে, তা বঙ্গবন্ধু নির্দেশনা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু অনেকবারই বলেছেন, ‘বিশ্ব আজ দুটি শিবিরে বিভক্ত। একটি হচ্ছে শোষক আর একটি হচ্ছে শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।’ তিনি বারবারই বলেছেন, বাংলাদেশ হবে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড। বাংলাদেশ সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে। কারও প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে না। বাংলাদেশ কারও সঙ্গে বৈরিতা সৃষ্টি করবে না। তবে বাংলাদেশ সর্বাবস্থায় তার স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখবে। ’৭০-এর দশকে এমন দৃঢ় উচ্চারণ সত্যি কঠিন ছিল। কথাটি বলা যত সহজ ছিল, বাস্তবায়ন করা তত সহজ ছিল না। বিশেষ করে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে, যখন বিশ্ব দুভাগে বিভক্ত ছিল।
স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ দৃশ্যত পশ্চিমা বিশ্বের বিরোধিতা এবং অসহযোগিতা প্রত্যক্ষ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। চীনের অবস্থানও ছিল মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে। এমন কি মধ্যপ্রচ্যের মুসলিম দেশগুলোর অবস্থানও বাংলাদেশের অনুকূলে ছিল না। এমনই এক অবস্থায় বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। কাজেই সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে একটি নতুন দেশের পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন করা বেশ কঠিন কাজই ছিল। সে সময় পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়, এমন উচ্চারণ করা বেশ সাহসী কাজ ছিল। একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই এমন সাহসী কথা উচ্চারণ করা সম্ভব ছিল।
বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সাহসিকতা এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করেছেন। তিনি কখনোই এমন কোনো কথা বলেননি যে, ওইসব দেশ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে কাজেই তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তিনি অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে তার পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন করেছেন। তিনি কখনোই বলেননি সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দিয়েছে, তাই আমরা সম্পূর্ণরূপে সোভিয়েত জোটে ঢুকে যাব। বিশ্বের খুব কম রাষ্ট্রনায়কের পক্ষেই এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। বঙ্গবন্ধু সম্পূর্ণ বৈরী পরিস্থিতিতে তার পররাষ্ট্রনীতি তৈরি করেছেন। বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগতভাবে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে কথা বলেছেন। আবার সেটাকে রাষ্ট্রীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এভাবে তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির একটি তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক কাঠামো তৈরি করেন। বঙ্গবন্ধু যে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেছেন তা এখনো সমকালীন।
পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু যখন লন্ডন গমন করেন, তখন সেখানকার সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ভবিষ্যতে তিনি কী ধরনের সাহায্য চান বা বাংলাদেশের ব্যাপারে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা কী হবে? বঙ্গবন্ধু তখন বলেছেন, বাংলাদেশের মানুষ সংগ্রাম করেছে। তারা সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশের মানুষ যে ধরনের নিপীড়ন সহ্য করেছে তাতে বৃহৎ শক্তিবর্গের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের পাশে দাঁড়ানো। বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অর্থনৈতিক দিক থেকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা চাই বিশ্ব আমাদের পাশে দাঁড়াবে। তবে তিনি আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে কোনো সহায়তা চাননি। শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধু চেষ্টা করেছিলেন বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে একটি আত্মমর্যাদাপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে ‘বটম লেস বাস্কেট’ বলেছেন। সে দেশের আত্মমর্যাদাকে সমুন্নত রেখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে সফল হয়েছিলেন।
বঙ্গবন্ধু তার শাসনকালে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সামিটে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে যান জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে। এ সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্ব নেতারা জানতে পারেন বঙ্গবন্ধু কেমন জাতীয়তাবাদী, আপসহীন সংগ্রামী নেতা। বিশ্ব নেতারা আরও জানতে পারেন বঙ্গবন্ধু কেমন মানবিক গুণসম্পন্ন একজন নেতা। এ সম্মেলনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রো, আলজেরিয়ার হুয়ারি বুমেদিন, প্যালেস্টাইনের ইয়াসির আরাফাত প্রমুখ বিশ্ব নেতার সংস্পর্শে আসতে সক্ষম হন। এ সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্ব নেতারা বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস জানতে পারেন। বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যুক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্সে (ওআইসি) যোগাদান করেন। ওআইসি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর যোগদান ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা।
উল্লেখ্য, লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে যোগদানের এক দিন আগে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে। পাকিস্তানের কাছে স্বীকৃতি আদায় করাটা যে কোনো বিচারেই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু। লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে দেয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণ মুসলিম নেতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণ দেন। এটি একটি মাইলফলক হয়ে আছে। জাতিসঙ্গের এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের কথা বলেছেন। বলেছেন প্যালেস্টাইনিদের ওপর ইসরায়েলের বর্বর নির্যাতনের কথা। বিশ্ব নেতাদের সেদিন একজন মানবতাবাদী নেতার অবস্থান প্রত্যক্ষ করেন। বঙ্গবন্ধু তার পররাষ্ট্রনীতি এখানে সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। ১৯৭৫ সালে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথের বৈঠকে তিনি অংশগ্রহণ করেন। এসব আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু তার পররাষ্ট্রনীতি এবং চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরেন। বঙ্গবন্ধু তার সাড়ে ৩ বছরের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকালে তার পররাষ্ট্রনীতির সফল বাস্তবায়ন করেছেন। বাংলাদেশকে তিনি একটি নেতৃত্বের স্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু ছিলেন শতভাগ সফল, এ ব্যাপারে কারও কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে তিনি সর্বোচ্চ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন।
বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যত দ্রুত সম্ভব বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় করা। বঙ্গবন্ধু জানতেন স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা বেশি কঠিন। তাই তিনি বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায়ের বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বাংলাদেশকে অত্যন্ত বিরূপ পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছিল। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সৌদি আরবসহ অন্যান্য আরব দেশ বিরোধিতা করে আসছিল। সেই অবস্থায় বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায় করা বেশ কঠিন ছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন এবং আত্মমর্যাদাপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য এবং ১৯৭৩ সালের মধ্যেই তিনি এই কাজটি সূচারুভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। এ সময়ের মধ্যে বিশ্বের ৫০টিরও বেশি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। চীনের ভেটোর কারণে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ না পেলেও অনেক বড় বড় আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ বাংলাদেশ লাভ করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত করানোর জন্য তিনি মুসলিম বিশ্বের স্বীকৃতি লাভের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মুসলিম বিশ্ব বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করত। বঙ্গবন্ধু সেই ভুল ধারণা ভেঙে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির আরেকটি বড় সাফল্য হচ্ছে যুদ্ধাবসানের মাত্র তিন মাসের মধ্যেই ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের স্বদেশে ফেরত পাঠানো। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো মিত্রবাহিনী এত স্বল্প সময়ে স্বাধীন দেশ থেকে প্রত্যাহার করা হয়নি। বিশ্বের শত শত বছরের ইতিহাস ঘাটলেও এ ধরনের একটি উদাহরণ দেয়া যাবে না, যেখানে মাত্র তিন মাসের মাথায় মিত্রবাহিনী স্বাধীন দেশ ত্যাগ করেছে। বঙ্গবন্ধু এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করেছেন।
আমরা দেখেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রবাহিনী যেসব দেশকে মুক্ত করেছে, তাদের বিরক্ত করে ছেড়েছে। জার্মানিকে বিভক্ত করা হয়েছে। কোরিয়াকে বিভক্ত করা হয়েছে। স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর ব্যাপক সহায়তা ছিল। ভারতীয় বাহিনীর সহায়তা বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কোনো ধরনের শক্তি প্রয়োগ বা মনোমালিন্য সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতীয় বাহিনীকে প্রত্যাহার করানো হয়নি। বরং পরস্পর সুসম্পর্ক বজায় রেখেই ভারতীয় বাহিনীকে স্বদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয় মিত্রবাহিনীকে স্বদেশে প্রেরণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু অসাধারণ কূটনৈতিক সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর প্রতি মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর অগাধ আস্থা ছিল। তাই তিনি বঙ্গবন্ধুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেননি। তবে এ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ়তা এবং কূটনৈতিক দক্ষতা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। এত অল্প সময়ে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এমন সাফল্য বিশ্বে খুব কম রাষ্ট্রনায়কেরই আছে। বঙ্গবন্ধু তার পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে খুব অল্প সময়ে বাংলাদেশকে বিশ্বে পরিচিত করাতে সমর্থ হয়েছেন। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সহায়তা লাভ করেছেন। বিশেষ করে ভারত, সোভিয়েত রাশিয়া ইত্যাদি দেশ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সহায়তা করেছে। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য সহায়তা দেয়ার কথা বলে সেই খাদ্য সহায়তা দেয়নি। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় করাটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে।
এমনকি পাকিস্তান বাহিনীর সহায়তার জন্য সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করেছিল, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধু সেই পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। পশ্চিমা বিশ্ব, জাপান, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম বিশ্বের স্বীকৃতি অর্জন এবং তাদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সহায়তা লাভ একটি বিরল ঘটনা। বঙ্গবন্ধু তার স্বল্পকালীন শাসনামলে এই সাফল্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়া কর্ণফুলী নদীতে মাইন ক্লিন করার ক্ষেত্রে যেভাবে সহায়তা করেছে, তা উল্লেখের দাবি রাখে। মুসলিম বিশ্ব থেকেও সাহায্য এসেছে। এমন কি চীনের সঙ্গে এক ধরনের অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সময়ে। পরাশক্তি থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শরিক করা এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু সমুদ্র আইন প্রণয়ন করেছিলেন। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বিষয়টি বঙ্গবন্ধু তখনই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।
লাহোরে ওআইসি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর যোগদানের বিষয়টি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও মন্ত্রিপরিষদের কেউ কেউ এর বিরোধিতা করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু লাহোরে ওআইসি সম্মেলনে যোগদানের এক দিন আগেই পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বঙ্গবন্ধু এই সম্মেলনে যোগদান না করলে পাকিস্তানের স্বীকৃতি পেতে আরও বিলম্ব হতো। এ ছাড়া এই সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু মুসলিম বিশ্বের নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হন। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বে যে ভুল ধারণা ছিল, তা দূরীভূত হয়। লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর অংশগ্রহণ ছিল আবেগ বিবর্জিত এবং অত্যন্ত বাস্তবসম্মত একটি সিদ্ধান্ত। বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদের অনেকেই হয়তো বঙ্গবন্ধুর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু বঙ্গবন্ধু তার সিদ্ধান্তে ছিলেন অটল। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের দ্বিমতটাকে অতিক্রম করে সম্মেলনে যোগদান করাটাই হচ্ছে যোগ্য নেতৃত্বের পরিচায়ক। বঙ্গবন্ধু সব সময় শুধু নিজের ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিতেন না, তিনি অন্যের ইচ্ছাকেও গুরুত্ব দিতেন। এটাই হচ্ছে প্রকৃত নেতার যোগ্যতা। বঙ্গবন্ধু অন্যদের ভাবনাকে গুরুত্ব দিতেন একই সঙ্গে তার ভাবনা যে অন্যদের চেয়ে শ্রেয় সেটাও প্রমাণ করতেন।
বঙ্গবন্ধু যে অত্যন্ত যোগ্য এবং প্রজ্ঞাবান একজন নেতা, তা তার পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ করলেই অনুধাবন করা যায়। বঙ্গবন্ধু শুধু মুসলিম বিশ্বের স্বীকৃতি আদায় করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি নিজেকে মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্যালেস্টাইনের সমস্যা থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধু আরব বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক ফোরামে সবসময়ই সোচ্চার থেকেছেন। মুসলিম নেতারাও বঙ্গবন্ধুর প্রতি খুবই আন্তরিক ছিলেন। তারা বঙ্গবন্ধুর ভয়েসটাকে গুরুত্ব দিতেন। মুসলিম বিশ্বে এবং অন্যান্য কোনো কোনো দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে যে ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল, বঙ্গবন্ধু তা তিরোহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিউবার নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন, আমি হিমালয় দেখিনি, আমি বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি। তার এই মন্তব্যই প্রমাণ করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান কেমন ছিল।
বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মূলকথাই ছিল আত্মমর্যাদা সম্মুন্নত রেখে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব নিশ্চিত করা। তিনি স্বাধীনতাযুদ্ধে সহায়তাকারী দেশগুলোর পাশাপাশি যারা বিরোধিতা করেছিল, তাদের সঙ্গেও সম্পর্ক উন্নয়নে ব্রতী হন। তিনি এক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে সফলতা অর্জন করেছিলেন। ‘সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়’ বঙ্গবন্ধুর এই পররাষ্ট্রনীতি ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং বাস্তবধর্মী। বর্তমান সরকারও বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথেই পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করে চলেছেন। বঙ্গবন্ধু বিশ্বে বাংলাদেশকে একটি আত্ম মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জনগণের যে আত্মত্যাগ বঙ্গবন্ধু তাকে বৈশ্বিকভাবে তুলে ধরেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে মানবতার একটি ধারা সবসময়ই প্রবাহমান ছিল। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে জাতিসংঘে প্রথম বাংলা ভাষায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার প্রতিটি ছত্রে মানবতার কথা বিধৃত হয়েছিল।
একটি সদ্য স্বাধীন দেশের সরকারপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে সাফল্য প্রদর্শন করেছেন, তা সত্যি বিস্ময়কর। তিনি বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন। যে দেশ নিজেদের স্বাধীনতার রক্ষার পাশাপাশি অন্য দেশের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকেও গুরুত্ব দিতে জানে। বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথেই পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করছে। ফলে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ একটি মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সদস্য, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।
অনুলিখন: এম এ খালেক


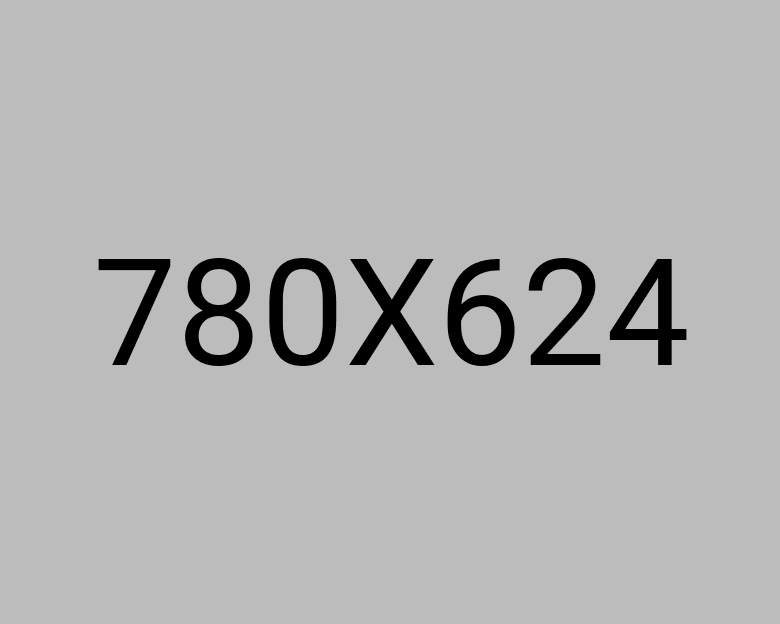
মতামত দিন
মন্তব্য করতে প্রথমে আপনাকে লগইন করতে হবে