উদ্বোধনী সংখ্যা ৪ : সম্ভাবনার বাংলাদেশ
ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত এবং অর্থনীতির হালের গতি-প্রকৃতি

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যে অর্জন করেছে, তা বৈরী রাজনীতি সত্ত্বেও এক কথায় চমকপ্রদ। এ কথা ঠিক যে, দীর্ঘ একটা সময় মুক্তিযুদ্ধের যে অর্থনীতি বাংলাদেশ চালু করেছিল, তা ওই রাজনৈতিক চাপে বিপর্যস্ত এবং বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই সময়টায় যে গরিব হিতৈষী, কৃষিবান্ধব, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাবান্ধব যে অর্থনীতি বাংলাদেশে চালু হয়েছিল, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সেটা ১৯৭৫-পরবতী সময়ে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। মাত্র ৯৩ মার্কিন ডলার মাথাপিছু আয় নিয়ে যে অর্থনীতি যাত্রা শুরু করেছিল, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সাড়ে তিন বছরেই তা প্রায় ২৬০ ডলারে উন্নীত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর তার শারীরিক অনুপস্থিতিতে দেশ আবারও পিছিয়ে যেতে থাকে। অর্থনীতি উল্টোপথে চলতে শুরু করে। মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় পরের বছরই (১৯৭৬) ১৩৮ মার্কিন ডলারে নেমে আসে। পরের বছরে তা আরও একটু কমে ১২৮ মার্কিন ডলারে নেমে আসে। দীর্ঘ ১৩টি বছর লেগেছিল আমাদের সেই আগের পর্যায়ে পৌঁছুতে। এর পরেও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল।
১৯৯০ সালের পর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হলে বাংলাদেশের অর্থনীতি আবার জেগে উঠতে শুরু করে। তবে সেটা পুরোপুরি জেগে ওঠা বলা যাবে না। এ কথাও ঠিক, বেশ কিছু সংস্কার হাতে নেয়া হয়েছিল। তবুও অর্থনীতিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক বলা যাচ্ছিল না। ১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হবার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিধৃত অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম ফের শুরু হয়। সেই উন্নয়নের অংশ হিসেবে গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়েছে। ২০০৮ এর দিকে মাথাপিছু গড় জাতীয় আয়ছিল ৭০০ মার্কিন ডলারের মতো। এখন গড় মাথাপিছু জাতীয় আয় প্রায় ২ হাজার ৮০০ মার্কিন ডলারে উপনীত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় পাকিস্তানের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণের মতো। অথচ ১৯৭২ সালের পাকিস্তানের মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় আমাদের চেয়ে ৬০ শতাংশ বেশি ছিল। মাথাপিছু গড় জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে আমরা ২০১৫ সালেই পাকিস্তানকে অতিক্রম করে এসেছি। এমনকি গত চার বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষের গড় জাতীয় আয় ভারতের চেয়েও বেশি।
মূলত দুটি কারণে এই বিস্ময়কর অর্জন সম্ভব হয়েছে। প্রথমত, কৃষি, রপ্তানি এবং জনশক্তি রপ্তানি খাত আমাদের শক্তি জুগিয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কাজটি বঙ্গবন্ধুই প্রথম শুরু করেছিলেন। ১৯৭২ সালে মোট ফার্টিলিটি রেট ছিল অনেক বেশি। একটি পরিবারে গড়ে ৬ থেকে ৭টি সন্তান ছিল। এখন পরিবারপ্রতি সন্তান জন্মদানের হার হচ্ছে ২টি। মূলত এ কারণেই মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে জনসংখ্যা কমে যাবার কারণে আমরা যেমন খুশি তেমনি আবার শঙ্কিতও বটে। জাপান বা এ ধরনের আরও কিছু দেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের মতোই ভালো করছিল; কিন্তু যখন তাদের জনসংখ্যা কমতে শুরু করে, তখন এক পর্যায়ে তাদের মাথাপিছু গড় জাতীয় আয়ও কমতে শুরু করে। খুব বেশি দিন নয়। বড়জোড় ২ দশক আমরা মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় এখনকার মতো বাড়িয়ে যেতে পারব। বর্তমানে আমাদের যে জনশক্তি আছে, তাকে যদি আরও দক্ষ এবং প্রযুক্তি-নির্ভর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও দক্ষ করে তুলতে পারি, তাহলে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুফল আমরা নিশ্চয় ভোগ করতে পারব। এ জন্য আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও কর্মমুখী করে গড়ে তুলতে হবে।
আমরা চিন্তিত এ জন্য যে, আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা গুণগত মানসম্পন্ন উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তুলতে পারছে না। অদক্ষ জনশক্তি নিয়ে কখনোই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকা সম্ভব নয়। বর্তমানে যে প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, সেখানে অনেকসংখ্যক মানুষকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। কয়েকদিন আগে একটি জরিপে তরুণরা বলেছেন তাদের অন্তত ৪২ শতাংশ দেশেই থাকতে চান না। তারা জানিয়েছেন তারা যেভাবে গুণমানের শিক্ষক ছাড়াই লেখাপড়া করেছে, তা দিয়ে চাকরি বা কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে না। তাই শিক্ষিত তরুণদের ব্যাপক অংশ বেকার থেকে যাচ্ছে। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত বেকার তৈরির কারখানা। মূলত এ কারণেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য বিশেষ জোর দিতে হবে। তাই শিক্ষকের মান ও মর্যাদা বাড়ানোর ওপর জোর দিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত এবং কার্যকর করা গেলেই আমাদের উন্নয়ন টেকসই হবে।
গত ৫২ বছরে আমাদের দেশ শুধু মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় অর্জনের ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে, তা নয় একই সময়ে দেশের অর্থনীতির আকার এবং পরিধি দুইই বেড়েছে ব্যাপকভাবে। ১৯৭২-১৯৭৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির সার্বিক আকার ছিল ৬ দশমিক ২৩ (অন্য মতে ৮) বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেখান থেকে আজকে অর্থনীতির আকার ৪৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উপনীত হয়েছে। এটা অবশ্যই উৎসাহব্যাঞ্জক। সম্প্রতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিইবিআর বলেছে আর ১৫ (পনেরো) বছর পরেই বাংলাদেশ পৃথিবীর ২০তম অর্থনীতি হয়ে যাবে; কিন্তু আমি পুরোপুরি খুশি নই এ জন্য যে, আমরা আরও ভালো করতে পারতাম, যদি মাঝখানে আমাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেক সময় আমরা না হারাতাম। বর্তমান প্রবৃদ্ধির যে ধারা, তা টেকসই করতে হলে আমাদের জনশক্তির দক্ষতা বাড়াতে হবে। দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলা না গেলে উন্নয়ন সম্ভাবনা পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগানো যাবে না। জনশক্তিই যে আমাদের প্রধান সম্পদ– এ কথাটি নীতিনির্ধারকদের মানতে হবে এবং তাকে সযত্নে বিকশিত করতে হবে।
তাছাড়া, যে আমাদের খুব জরুরিভাবে যে কাজটি করতে হবে, তাহলো উদ্যোক্তা তৈরি করা। উদ্যোক্তাদের সাহস, পুঁজি এবং বাজরের সুযোগ করে দেয়ার মতো একটি পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। একজন উচ্চ শিক্ষা লাভের পর তিনি কেন চাকরির পেছনে ঘুরবেন। তিনি তো উদ্যোক্তা হিসেবে তার ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার বলেছেন, ‘চাকরির পেছনে আপনারা ঘুরবেন কেন? উদ্যোক্তা হোন। তখন আপনারাই অন্যদের চাকরি দিতে পারবেন।’ বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল দেশে শুধু সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি দিয়ে কখনোই বেকার সমস্যা দূর করা যাবে না। এ জন্য সবার আগে প্রয়োজন বিপুলসংখ্যক উদ্যোক্তা তৈরি করা। বাংলাদেশের যুবকদের মাঝে উদ্যোক্তা হবার মতো সহজাত গুণাবলি আছে। প্রয়োজন শুধু তাদের ভেতরের শক্তিটাকে জাগিয়ে তোলা এবং তাদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। ভারত গত তিন-চার বছরে শূন্য থেকে প্রায় ১ লাখ স্টার্টআপ তৈরি করতে পেরেছে। আমরা কিন্তু কয়েক হাজার স্টার্টআপ তৈরি করে উঠতে পারিনি। পরিবেশবান্ধব উদ্যোক্তা তৈরি করা আমাদের জন্য খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।
আমরা যদি উদ্যোক্তা তৈরি করতে পারি, তাহলে এসব ছেলেমেয়েই আমাদের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে। উদ্যোক্তা কেমন করে তৈরি করব, স্টার্টআপ কেমন করে হবে, তা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। স্টার্টআপ কিন্তু সব সময় সরকার করতে পারে না। স্টার্টআপ তৈরি করার জন্য ব্যক্তি খাত ও সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে পরিবারকে এগিয়ে আসতে হবে। মা-বাবা যদি এগিয়ে না আসে, তাহলে তারা যদি না চান যে, ছেলেমেয়ে উদ্যোক্তা হোক তাহলে তারা কিন্তু চাকরির পেছনেই ঘুরতে থাকবে। এই তরুণ সম্প্রদায়কে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে। সমাজে অনেক পুঁজি আছে, এটাকে বলা হয় এঞ্জেল ক্যাপিটাল। এ ধরনের পুঁজি শুধু সমাজের জন্য কাজ করে। সেরকম পুঁজি আমাদের দেশেও আছে। কিন্তু আমরা সেই পুঁজিকে সংগঠিত করতে পারছি না। কিছু কিছু পুঁজি আমরা সংগঠিত করছি। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল হিসেবে তা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংগ্রহ করছি; কিন্তু সেটা পর্যাপ্ত নয়। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যারা শুধু এঞ্জেল ক্যাপিটাল নিয়ে কাজ করে। তাদের আরও উৎসহিত করতে হবে। আমাদের এই ঢাকা শহরেই এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাদের সন্তানাদি বিদেশে থাকে। তারা আর কখনোই হয়তো দেশে ফিরে আসবে না। তাদের বাড়িগুলো বিক্রিও করতে পারছেন না।
আইনের বেড়াজালের কারণে বিক্রি করলেও সে টাকা আনুষ্ঠানিক পথে বিদেশে নিতে পারছে না। এই বাড়িগুলো বিক্রি করে যদি তাদের মূল্যের একটা অংশ স্টার্টআপ ক্যাপিটালে বিনিয়োগের সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে তারা দীর্ঘ মেয়াদি সুবিধা পেতে পারে। তাদের এই অর্থ স্টার্টআপ উদ্যোগে অর্থের সংকুলান করতে পরবে। পাশাপাশি তারা দীর্ঘ মেয়াদে আর্থিক সুবিধা পেতে পারবেন। কর সুবিধাও পেতে পারেন। এ ধরনের নতুন চিন্তাভাবনার সুযোগ আছে। আমরা আশা করব, জাতীয় নির্বাচনের পর এ ধরনের কিছু নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। নতুন সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি। আমাদের দেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অবকাঠামোগত খাতে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। এই উন্নয়নের কথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। তবে অবকাঠামোগত উন্নয়নকে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগাতে হবে। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ গেছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে টেকসই করার জন্য আমাদের সবুজ বিদ্যুতের দিকেও নজর দিতে হবে। অন্যদিকে যে বিদ্যুৎ আমরা উৎপাদন করছি, তার যেন যথার্থ ব্যবহার হয়, সে দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে।
বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের ১৫/২০ শতাংশ উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাবহৃত থাকতে পারে; কিন্তু ৫০-৬০ শতাংশ উৎপাদন ক্ষমতা যদি অব্যাবহৃত থাকে, তাহলে সেই প্ল্যান্ট কখনোই টেকসই করা যাবে না। বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট বসিয়ে দিনের পর দিন রেখে ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়ে যাবেন তা তো হতে পারে না। কাজেই আমাদের টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেলসহ বড় বড় যেসব অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলোর সুফল আমরা ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছি। ট্যানেলের সুবিধা পাচ্ছি। এক্সপ্রেসওয়ের সুবিধা পাচ্ছি। এগুলো যাতে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়, তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। তবে এখন নতুন প্রকল্প গ্রহণের আগে আমাদের চিন্তা করতে হবে আমাদের সামাজিক অর্থনীতি কতটা তা সাপোর্ট করতে পারবে। আমরা কত পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতে পারছি এবং বিদেশ থেকে কতটা ঋণ পাচ্ছি, তার আলোকে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। বাদ বিচার ছাড়াই যেনতেনভাবে প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত হবে না। ২০২২ সালে যখন জ্বালানি তেলের মূল্য অনেকটাই বৃদ্ধি পেল এবং একই সঙ্গে টাকার অবমূল্যায়ন ঘটল, তখন আমাদের সামাজিক অর্থনীতি খানিকটা চাপের মধ্যে পড়ে। এখনো সেই চাপ থেকে আমরা পুরোপুরি উদ্ধার পেয়েছি তা বলা যাবে না।
আয় বুঝে ব্যয় করার ব্যাপারে আমাদের খুবই সাবধান থাকতে হবে রাজস্বের জোগান ও ব্যবহারের ‘মিচম্যাস’ যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে। আমরা রাজস্ব এবং ম্যাক্রো ইকোনমি যতটা চাপ নিতে পারবে, সেই পরিমাণ প্রকল্প আমরা গ্রহণ করব। আর একটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে, তাহলো যে উন্নয়ন ঘটছে, তা যেন টেকসই হয়। আমাদের অর্থনীতিতে যে প্রবৃদ্ধি ঘটছে, তাও কিন্তু কম নয়; বিশ্ব অর্থনীতিতে ২০২৩ সালে ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে। আর বাংলাদেশে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে বলে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পূর্বাভাস দিয়েছে। আর আমরা বলছি এ বছর বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের নিচে হবে না। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে প্রবৃদ্ধি নিয়ে প্রতি বছরই কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এটাই স্বাভাবিক। আর আমরা কিন্তু অর্থনীতির সব সেক্টরকে হিসাবেও আনতে পারি না। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে এবং গ্রামে-গঞ্জে যে কাজ হয় তার একটা অংশ হিসাবের বাইরেই থেকে যাচ্ছে। তাই আমাদের জিডিপির পুরো চিত্র আমরা পাই না, দারিদ্র্য বিমোচনে আমরা বড় ভূমিকা পালন করেছি। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৮০ শতাংশ। এখন তা থেকে ১৮ শতাংশে নেমে এসেছে। এটি একটি বিরাট অর্জন। এ ধরনের অর্জনই একটি দেশের জন্য অনেক কিছু।
আমরা অর্থনীতির সব খাতেই ব্যাপক উন্নতি অর্জন করেছি। তবে আমাদের এখনই আত্মতৃপ্তিতে ভোগার কোনো সুযোগ নেই। এখনো অনেকেই হত দরিদ্র আছেন। আমাদের তাদের কথাও ভাবতে হবে। সব মিলিয়ে গরিবের সংখ্যা এখনো প্রায় ৩ কোটি। এই মানুষগুলোকে আমাদের উন্নয়নের মূল শ্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে। তবে আশার কথা যে, সামাজিক উন্নয়ন সূচকগুলোতেও (জীবনের গড় আয় শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার, পুষ্টির মান ইত্যাদি) আমাদের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। আনুষ্ঠানিক কাজে নারীর অংশগ্রহণ (প্রায় ৪৩%) এবং সমাজে ও প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ তাদের ক্ষমতায়নের সূচককেই পোক্ত করে চলেছে। তবে এত কিছু সাফল্য সত্ত্বেও হালে একটি সমস্যা আমাদের বড়ই বিপদের মধ্যে রেখেছে, তা হলো উচ্চ মূল্যস্ফীতি। গত অক্টোবর মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ। খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১২ দশমিক ৫০ শতাংশ। নভেম্বর মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে এসেছে। ডিসেম্বরে হয়তো আরেকটু কমবে। তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের আরও অনেক কিছু করণীয় আছে। বাংলাদেশ এখনো বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম খাদ্য আমদানিকারক দেশ বাংলাদেশ, যদিও আমাদের চাল আমদানি করতে হয় না; কিন্তু আমাদের গম আমদানি করতে হয়। ভোজ্যতেল আমদানি করতে হয়। শিশু খাদ্য আমদানি করতে হয়।
পেঁয়াজ-রসুন আমদানি করতে হয়। এই আমদানি করা পণ্য উৎপাদনে আমাদের কাজ করার আছে। কীভাবে এসব পণ্য আমদানি কমানো যায়, তা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে আমাদের সমুদ্র উপকূলে ফসল ফলানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশ যেসব খাদ্য পণ্য আমদানি করে, তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কাজেই এই ব্যয়বহুল খাদ্য পণ্যগুলো আমাদের স্থানীয়ভাবেই উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি আশপাশের দেশ থেকে সেগুলো আমদানির মধ্য মেয়াদি ‘কোটা’ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। আঞ্চলিক বাণিজ্যের সুযোগ আমাদের অবশ্যই নিতে হবে। আমরা নিঃসন্দেহে উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব পেয়েছি। এর পাশাপাশি আমরা যদি উপযুক্ত অর্থনৈতিক নেতৃত্ব পাই, তাহলে এই অর্জিত উন্নয়নের ধারাকে টেকসই করা সম্ভব। আমাদের বাজেটের প্রায় ২০ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় করা হয়। আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের একটি কৌশল আছে; কিন্তু সেই কৌশল আমরা এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পারিনি। এই কৌশল বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অপচয় রোধ করতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এর ডেলিভারি প্রক্রিয়ার স্তরে স্তরে ডিজিটাল ও সামাজিক মনিটর ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।
লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
অনুলিখন: এম এ খালেক


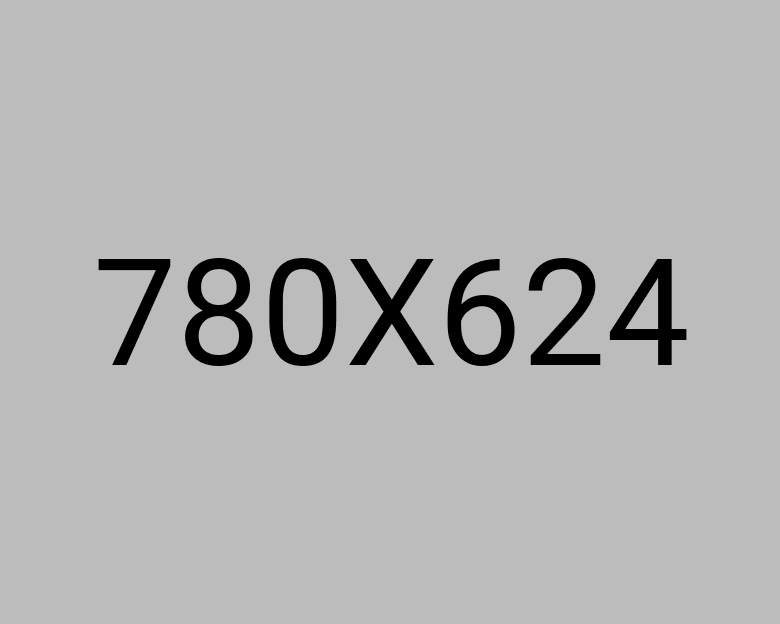
মতামত দিন
মন্তব্য করতে প্রথমে আপনাকে লগইন করতে হবে