ছোটবেলার ঈদ আনন্দ এখনো আমাকে স্মৃতিকাতর করে

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য যে দুটি সর্বজনীন আনন্দ-উৎসব রয়েছে, তার মধ্যে ঈদুল ফিতর যে কোনো বিবেচনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। এক মাস কঠোর সিয়াম সাধনার পর রোজা ভঙ্গের আনন্দই হচ্ছে ঈদুল ফিতর। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান নর-নারী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে ঈদুল ফিতরের জন্য। ইসলাম ধর্ম পাঁচটি আবশ্যিক মৌলিক স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলো হচ্ছে কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত। এর মধ্যে হজ শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল এবং যাকাত আর্থিক সামর্থ্যেরে ওপর নির্ভরশীল। অন্য তিনটি স্তম্ভ বান্দার শারীরিক সামর্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ‘ঈদ’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে আনন্দ। ইসলাম ধর্মে রোজা ফরজ হবার আগেও রোজা পালন করা হতো। তবে তা এতটা বরকতময় ছিল না। সম্প্রদায়ের এক মাস কঠোর সিয়াম সাধনার পর রোজা ভাঙার যে আনন্দ, সেটাই ঈদ। আক্ষরিক অর্থে ঈদ অর্থ আনন্দ।
রোজা শুধু সাধারণ একটি ইবাদত মাত্র নয়। এর মাধ্যমে বিত্তবানদের সম্যকভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয় ক্ষুধার্ত মানুষের যন্ত্রণা কতটা কষ্টদায়ক। রোজা বিত্তবান এবং বিত্তহীনকে একই কাতারে দাঁড় করায়। ইসলামের যেসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আছে, তার প্রতিটির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে বান্দার মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানব কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। ঈদের নামাজের মাধ্যমে এলাকার মানুষের মধ্যে মহা মিলনের একটি সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়। যারা সারা বছর এলাকার বাইরে থাকেন তারাও চেষ্টা করেন অন্তত ঈদের সময় এলাকায় গিয়ে আত্মীয়স্বজনসহ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। যারা এলাকা থেকে দূরে অবস্থান করেন তারা সুযোগ পেলেই ঈদের সময় গ্রামের বাড়িতে চলে যান।
ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর নানা ধরনের আনন্দময় স্মৃতি থাকে। আমার জীবনেও ঈদুল ফিতর ঘিরে আনন্দ-বেদনার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। অবসর সময়ে এসব ঈদ ম্মৃতি আমাকে আন্দোলিত করে। কখনো মনে হয় আবারও যদি ছোটবেলার সেই ঈদ আনন্দ ফিরে পেতাম তাহলে কতই না ভালো হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে ১৯৪২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ফেনীর অদূরে ধোনসাহদ্দা গ্রামে আমার জন্ম। তৎকালীন মহকুমা শহর ফেনীতে যখন বোমা নিক্ষিপ্ত হয় তখন আমার বয়স দুই বছরের বেশি হবে না। সেই সময় বোমার আঘাত থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্য মা ও দাদি আমাকে নিয়ে বেশ কয়েক বার খাটের নিচে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এ কথা আমি বহুবার শুনেছি। ভাই-বোনের মধ্যে আমি ছিলাম সবার বড়।
বাবা ছিলেন আইনজীবী, মা গৃহিণী। বাবা ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মানুষ। তিনি আমাদের সবাইকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন কিন্তু তার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটতো খুবই কম। আমরা বাবাকে সমীহ করে চলতাম। আমার জীবনে বাবাকে মাত্র তিনবার কাঁদতে দেখেছি। প্রথমবার বাবাকে কাঁদতে দেখি ১৯৬০ সালে যেদিন আমার দাদি মারা যান। দ্বিতীয়বার ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য যখন সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গমন করি। সেই সময় আমাকে বিদায় জানানোর সময় বাবা কেঁদেছিলেন। তৃতীয়বার দেশ স্বাধীন হবার পর আমি যখন ৫ জানুয়ারি ফেনীতে প্রবেশ করি, সেদিনও বাবাকে কাঁদতে দেখি। বাবা ছিলেন অত্যন্ত বলিষ্ঠ চরিত্রের একজন মানুষ। কোনো অন্যায় তিনি প্রশয় দিতেন না। নিজেও অন্যায় করতেন না।
আমাদের গ্রামটি বেশ বড় এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর ছিল। গ্রামীণ রীতি অনুযায়ী, আমার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বাড়িতে গৃহ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। এরপর তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হবার মাধ্যমে আমার আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শুরু হয়। স্কুলটি ফেনী শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে আমি ফেনী হাইস্কুল সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। স্কুলে ভর্তি হবার পর আমরা ফেনী শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করি; কিন্তু আমার দাদি তিনি স্বামীর ভিটে ছেড়ে ফেনী শহরে আসতে কোনোভাবেই রাজি হচ্ছিলেন না।
ছোটবেলায় আমি ছিলাম অত্যন্ত ক্ষীণ স্বাস্থ্যের অধিকারী। শারীরিক কারণে আমি কোনো খেলায় তেমন একটা অংশ গ্রহণের সুযোগ পেতাম না। কাজেই খেলাধুলায় ভালো করার জন্য কখনোই পুরস্কৃত হইনি। তবে প্রায় প্রতি বছরই আমি ভালো রেজাল্ট করার জন্য পুরস্কৃত হয়েছি। পুরস্কার হিসেবে বিখ্যাত লেখকদের বই দেয়া হতো। প্রতি বছর বার্ষিক পরীক্ষায় আমি ভালো ফল করতাম কিন্তু তা সত্ত্বেও স্কুলজীবন ছিল আমার কাছে নিরানন্দময় এবং একঘেয়েমিপূর্ণ। স্কুলে কোনো সহশিক্ষা কার্যক্রম ছিল না। তাই পাঠ্যবইরের বাইরের বই পড়ার মধ্যেই আমি আনন্দ খুঁজে পেতাম। এভাবে সেই ছোটবেলাতেই আমি বাংলা ভাষায় প্রসিদ্ধ সব সাহিত্যিকের অধিকাংশ সাহিত্য কর্ম পড়ে ফেলি।
আমাদের পারিবারিক অবস্থা বেশ ভালো ছিল। আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে তালুকদার ছিলাম। তৎকালীন সীমান্তের পূর্বাংশে জমিদারি প্রথা প্রচলিত ছিল। একইভাবে পশ্চিাঞ্চলীয় অংশে তালুকদারি প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট দিনে প্রজারা বার্ষিক রাজস্ব প্রদানের জন্য আমাদের বাড়িতে আসতেন। সেই সময় অত্যন্ত আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হতো। ভারত বিভক্ত হবার পর তৎকালীন পাকিস্তানে ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করা হলে আমাদের তালুকদারিও চলে যায়। আমরা যদিও এ জন্য ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলাম কিন্তু তালুকদারি চলে যাবার পর আমাদের আয়ের একটি বড় উৎস বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হলেও পশ্চিম পাকিস্তানে কিন্তু জমিদারি প্রথা বহাল থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে যারা জমিদার ছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। দেশ ভাগের পর তারা ভারতে চলে যান। আর এই অঞ্চলে যারা মুসলমান জমিদার ছিলেন তারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ছিলেন। ফলে আমাদের এখানে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা খুব একটা কঠিন হয়নি।
গ্রামীণ জীবনে আমাদের সময় কেটেছে অনেকটাই নিরানন্দ পরিবেশে। পারিবারিকভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের প্রতি জোর দেয়া হতো। বিশেষ করে রোজা রাখা এবং নিয়মিত নামাজ আদায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো। বাবা আমাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য উপদেশ দিতেন কিন্তু কখনোই এ ব্যাপারে জোরাজুরি করতেন না। আমার স্বাস্থ্য খারাপ ছিল বলে আমাকে রোজা রাখার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হতো। এ নিয়ে আমার দুঃখের অন্ত ছিল না। কারণ আমার সমবয়সীরা রোজা রাখত; কিন্তু আমাকে রোজা রাখতে দেয়া হতো না।
পারিবারিকভাবে আমরা ইসলামী আদর্শ নেমে চলার চেষ্টা করতাম। আমার মনে আছে, খুব ছোটবেলায় আমাদের গ্রামের মসজিদে ঈদের নামাজ হতো। এলাকার লোকজন দলবেঁধে ঈদের নামাজ আদায় করতে যেতেন। ঈদের কয়েকদিন আগে থেকেই অপেক্ষা করতাম কবে ঈদ হবে। এখনো স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে, ১৯৫২ সালে আমি যখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি তখন প্রথমবার বাবার হাত ধরে ঈদের নামাজ আদায় করার জন্য গমন করি। তার আগে আমি ঈদের নামাজ আদায় করার জন্য গিয়েছি কি না, তা মনে করতে পারি না। তখন আমি ফেনী শহরে আমাদের বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। প্রথম ঈদের নামাজ আদায়ের অনুভূতি সম্পর্কে আমি কোনো মন্তব্য করতে পারব না। কারণ সেই সময় আমি ঈদ কি, তা খুব একটা বুঝতাম না। আমার কাছে ঈদ ছিল শুধু আনন্দের উপলক্ষ মাত্র। তবে এটা আমার মনে আছে, প্রথম বার ঈদের নামাজ পড়তে গিয়ে আমি বেশ আনন্দিত হয়েছিলাম। ছোটবেলায় ঈদের আনন্দ ছিল অন্যরকম।
প্রত্যেক বাড়িতে ভালো ভালো রান্না হতো। সবাই খুব আনন্দ করে সেসব খাবার খেত। ঈদের আগের দিন ছোট ছোট বাচ্চারা দলবেঁধে ঈদের চাঁদ দেখার আনন্দ। যে আগে চাঁদ দেখতে পেতো সে যেন রাজ্য জয় করার মতো আনন্দ পেতো। ঈদের চাঁদ দেখার পর থেকে ঈদের আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেতো। বাড়ির সবার জন্য ঈদের উপহার হিসেবে নতুন জামা-জুতা কেনা হতো। আমরা ঈদের জামা-কাপড় লুকিয়ে রাখতাম। ঈদের দিন সকালবেলা গোসল করে নতুন জামা-কাপড় পরিধান করে বড়দের সঙ্গে ঈদের জামাতে গমন করতাম। মহিলারা গৃহে অবস্থান করে নানা ধরনের রান্নার আয়োজন করতেন। ঈদের সময় বিভিন্ন এলাকায় বাচ্চাদের ‘সালামি’ দেয়ার রীতি প্রচলিত আছে। যদিও আমাদের এলাকায় ব্যাপকভাবে ঈদের সালামি প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল না। কোনো কোনো পরিবারে ঈদের সালামি দেয়া হতো। আমি সালামি পেয়েছি সে কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে; কিন্তু সালামি বাবদ কত পেয়েছিলাম তা সঠিকভাবে মনে নেই। তবে কাগজের নোট যে পাইনি তা বেশ ভালোভাবেই মনে আছে।
ঈদের দিন সকালবেলা বাবা খুব তাড়া দিতেন দ্রুত তৈরি হয়ে নামাজ আদায়ের জন্য ঈদের মাঠে যাবার জন্য। মিজান ময়দান বলে আমাদের এলাকায় একটি বড় মাঠ ছিল সেখানে প্রতি বছর ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হতো। আমরা সেখানে ঈদের জামাতে অংশ নিতাম। ফেনী শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা জামাতে অংশ নিতেন। আমার মনে আছে ফেনী আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ওয়াবদুল হক সাহেব ঈদের জামাতে ইমামতি করতেন। মিজান ময়দানে প্রতি বছর বিশাল ঈদের জামাত হতো। মোনাজাত হতো খুবই দীর্ঘ সময় ধরে। মোনাজাতে মুসলিম উম্মাহ এবং দেশের উন্নতির জন্য দোয়া করা হতো। ঈদের আনুষ্ঠানিকতা আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। আমরা আত্মীয়-স্বজনের বাসায় বেড়াতে যেতাম। অন্যরাও আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসত। সব মিলিয়ে ঈদের দিন এক আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হতো। তৃতীয় শ্রেণিতে থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সময় আমি প্রতি বছরই বাবার হাত ধরে ঈদের জামাতে যেতাম। এখনো ঈদের জামাতে গেলে মনে হয় বাবা বুঝি আমার হাত ধরেই আছেন। এখন আমি সাধারণত বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করি। আমার ছেলে এবং বাড়ির ম্যানেজার জামাতে আমার সঙ্গী হয়ে থাকে। কলেজে ওঠার পর বাবার সঙ্গে বা বাবার হাত ধরে ঈদের জামাতে তেমন একটা যাওয়া হয়নি।
আমার বাবা এলাকার বিভিন্ন জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমার বাবা-মা দুজনই খুব ধর্মপ্রাণ ছিলেন কিন্তু ধর্মান্ধ ছিলেন না। তারা ছিলেন উদার মানসিকতার মানুষ। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে আমরা ছিলাম অনেকটাই স্বাধীন। একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের এখন ধর্ম-কর্ম পালন করতে হয়। তবে আমি এক সময় বামপন্থি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলাম। আমি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের ব্যাপারে উদার। অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করলে ভালোই লাগে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে পারিবারিক উদারতা পরবর্তী জীবনে আমার চলার পথে বিরাট অবদান রেখেছে। কিছু কিছু আচরণ বিদ্যালয়ে শেখা যায় না। এগুলো পরিবার থেকেই শিখে আসতে হয়। এ জন্যই বলা হয়, ‘ব্যবহারে বংশের পরিচয়।’ আমার মধ্যে যদি উদার মানসিকতা থেকে থাকে তা আমার পরিবার থেকেই হয়েছে। আমার বাবা-মা খুবই উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাদের সেই উদারতা হয়তো কিছুটা আমার মাঝেও সঞ্চারিত হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে একটি স্মৃতি আমি এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে চাই। তখন আমি এবং আমার মতো আরও অনেকে প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সেই সময় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের বিষয় আমাদের মাঝে খুব একটা আগ্রহ ছিল না। একবার ঈদের দিনে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে তাকে আমি পাইনি। জানতে পারলাম সে ঈদের নামাজ আদায় করতে গেছে। আমি ফিরে আসার সময় নিউমার্কেটের কাছে এসে তার দেখা পাই। আমি জানতে চাইলাম তুমি কোন জামাতে গিয়েছিলে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি এখানকার জামাতে ছিলাম। অর্থাৎ তিনি জামাতে যাননি। নিউমার্কেট এলাকাতেই হাঁটাহাটি করেছেন। তার বাড়িতে সবাই জানে সে ঈদের জামাতে গেছে। আসলে সে গিয়েছিল নিউমার্কেট এলাকায়। তিনি বলেন, ঈদ অনুষ্ঠান তার কাছে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ যে দেশের মানুষ খেতে পায় না, সে দেশে ঈদ পালন করে কি লাভ? আমি তার এই বক্তব্যে বেশ বিস্মিত হই। আগে গ্রামে থাকা অবস্থায় এক ধরনের ঈদ আনন্দ উপভোগ করতাম। এখন অন্যরকম ঈদ আনন্দ উপভোগ করছি।
আমি যদি আমার ঈদ আনন্দ বা অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাই, তাহলে বাহরাইনের কথা না বললেই নয়। আমি ২০০৩ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাহরাইনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করি। এই সময়ে আমি ঈদ উদযাপনের যে অভিজ্ঞতা অর্জন করি, তা চিরদিন আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে। বাহরাইনে রাষ্ট্রদূত থাকা অবস্থায় দূতাবাসের উদ্যোগে প্রতি ঈদে বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান দুপর্বে বিভক্ত থাকত। প্রথম পর্বে ভিআইপিদের আপ্যায়িত করা হতো। বাহরাইনে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা ঈদের দিন আমন্ত্রিত হয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসে আসতেন। তাদের মোগলাই পরোটা এবং মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়িত করা হতো। দ্বিতীয় পর্ব সবার জন্য উন্মুক্ত থাকত। বাহরাইনে কর্মরত বাংলাদেশি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাতে যোগদান করতেন। তখন এক আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হতো। মনে হতো দূতাবাস যেন মিনি বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। এভাবে ঈদ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ইতিবাচক ইমেজ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এখনো ঈদ আনন্দ করি; কিন্তু সেই ছোটবেলার মতো ঈদ আনন্দ এখন আর খুঁজে পাই না।
ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী: সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক রাষ্ট্রদূত।
অনুলিখন: এম এ খালেক।


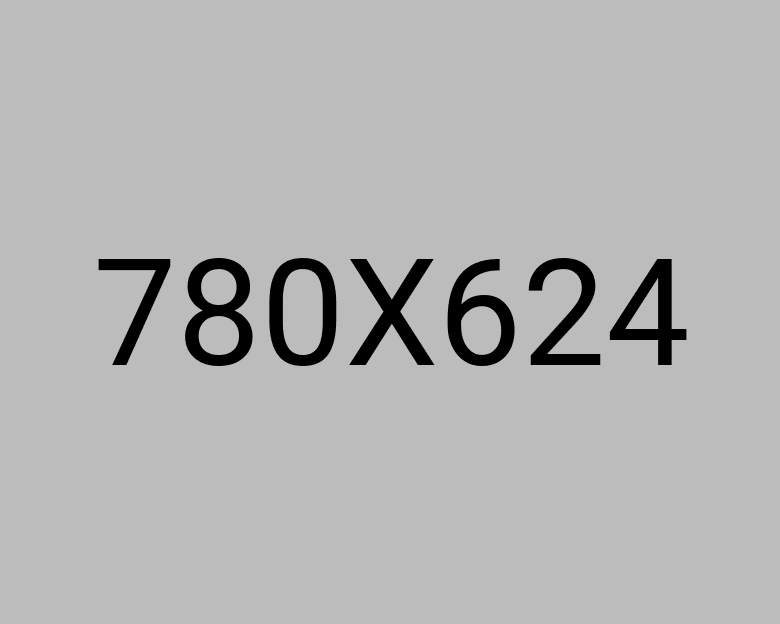
মতামত দিন
মন্তব্য করতে প্রথমে আপনাকে লগইন করতে হবে