সামাজিক ন্যায়ের যুক্তিতেই কোটা প্রয়োজন

সংরক্ষণ বা কোটা নিয়ে সারা দেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রার্থীরা প্রতিদিনই রাজপথে অবরোধ-বিক্ষোভ করছেন। ঢাকা শহরে গত কয়েকদিন ধরেই অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ ও অবরোধের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে সীমাহীন যানজট। সবার সব ক্ষোভ গিয়ে জমা হচ্ছে সরকারের ওপর। কোটা ইস্যুতে লাগাতার আন্দোলনে দুর্ভোগে পড়া মানুষজনের প্রশ্ন, সরকার কেন কোটা সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসছে না? এদিকে সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা বলছেন, কোটা বাতিল করা না-করার সিদ্ধান্তটি বর্তমানে উচ্চ আদালতে বিচারাধীন আছে। এটা ফয়সালা করবে আদালত। সরকারের এ ব্যাপারে কোনো কিছু করার নেই।
উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে প্রচলিত কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। এক পর্যায়ে সরকার কোটা প্রথা বাতিলও করে। তবে সম্প্রতি কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের কোটা-বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। প্রতিবাদে আবারও শুরু হয়েছে আন্দোলন। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সমতার ভিত্তিতে এগিয়ে নিতে কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধায় সারা বিশ্বে কোটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রচলিত। বাংলাদেশেও মুক্তিযুদ্ধের পর থেকেই এই ব্যবস্থা চালু হয়। মূলত সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিতের মাধ্যমে তাদের জনসংখ্যার মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনতে কোটাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। যদিও কোটা কোনো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। এটি অনিবার্যও নয়।
একটি দেশের সার্বিক অবস্থা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ নানা কাঠামোর ওপর নির্ভর করে কোনো জনগোষ্ঠীর জন্য কোটা ও বিশেষ সুবিধা বরাদ্দ করা হয়। ওই জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নতি হলে বিভিন্ন সময় এই ব্যবস্থায় সংস্কার করা হয়। আমাদের দেশেও একাধিকবার হয়েছে। কারও জন্য কোটা বা সংরক্ষণ প্রয়োজন নেই- এটা মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও দেশে প্রায় ৪ কোটি মানুষ দরিদ্রসীমার নিচে বাস করছে। তাদের উন্নতির জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতেই হবে। ৫০ শতাংশের বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না- এই যুক্তিও ঠিক নয়। ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যে এখনো ৬৮ শতাংশ সংরক্ষণ রয়েছে। এদেশে মুক্তিযোদ্ধা, নারী, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী, দলিতসহ একটা বৃহৎ অংশের মানুষের কাছে সংরক্ষণের বিশেষ সুবিধা এখনো পৌঁছায়নি। তারা এখনো দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবে আছেন। তাদের জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন রয়েছে।
স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের তৎকালীন নীতিনির্ধারকরা বহু যুগের শোষণ, বঞ্চনা ও আনুষঙ্গিক অন্যায়ের প্রতিকার করার পথ হিসেবে সংরক্ষণকে বেছে নিয়েছিলেন। সংরক্ষণ মূলে রয়েছে ‘অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন।’ এর দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ জাস্টিস বা বণ্টনের ন্যায্যতার তত্ত্বে। এই তত্ত্বের মূল সুর হচ্ছে: ভাগ্যের কারণে যেন কাউকে বঞ্চিত না হতে হয়। মুক্তিযোদ্ধা, নারী, প্রতিবন্ধী ও দলিতরা দীর্ঘ কাল ধরে উন্নয়নের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার বাইরে রয়ে গেছে। শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, পেশা বাছাইয়ের স্বাধীনতায়, বহু প্রজন্ম ধরে এই জনগোষ্ঠী উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত। এটা এমন এক দুর্ভাগ্য, যার ওপর নিজের তাদের বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ নেই। এই বঞ্চনা থেকে তাদের বের করে আনার জন্যই সংরক্ষণ। মুক্তিযোদ্ধারা দেশের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন। তাদের পরিবারের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষাদীক্ষা, সুযোগ-সুবিধায় পিছিয়ে থাকা নারী ও অনগ্রসর আদিবাসীদের জন্য যেমন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে, তেমনই আছে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রেও।
এটা বিশেষ সামাজিক ন্যায়ের যুক্তিতে করা হয়েছে। কেউ মদ খেয়ে, অথবা জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত হলে, বা ব্যবসায় কারও ভরাডুবি হলে কিন্তু সরকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে না। কথাটা হাস্যকর ঠেকতে পারে। হাসির কথা কিন্তু নয়। কোনো দুর্ভাগ্য নিজের তৈরি করা, অর্থাৎ যাকে এড়ানো যায় বা যেত, আর কোনো দুর্ভাগ্যের ওপর নিজের কোনো হাত থাকা সম্ভব নয়, অর্থাৎ যা এড়ানো অসম্ভব- ন্যায্যতার বিচারে সেটা মস্ত প্রশ্ন। যে দুর্ভাগ্য নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, একমাত্র তাতেই সংরক্ষণের দাবি করা যায়।
‘সংরক্ষণ’ আসলে একটা রাষ্ট্রীয় প্রায়শ্চিত্ত। ক্ষতিপূরণ। কিছু জনগোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট পরিচিতির কারণেই দীর্ঘকাল অপর (ক্ষমতাবান) জনগোষ্ঠীর হাতে বৈষম্যের শিকার, এবং সেই কারণেই অর্থনীতির বিভিন্ন স্তরে তাদের প্রতিনিধিত্ব স্বাভাবিকের চেয়ে কম- এই ভুলটা শুধরে দেওয়া ছাড়া সংরক্ষণের আর কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না। ফলে, সংরক্ষণের আওতায় আসতে হলে শুধু দুর্ভাগ্যের শিকার হলেই চলবে না, সেই দুর্ভাগ্য হতে হবে সমষ্টিগত ভূমিকা ও পরিচিতির কারণে এবং সংরক্ষণ যে পাল্টা বৈষম্য তৈরি করে- অর্থাৎ, ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চিতদের বাড়তি সুযোগ করে দেয় তথাকথিত গরিষ্ঠদের সুযোগ থেকে খানিকটা কেড়ে নিয়ে- ইতিহাসের কারণেই তাকে মেনে নেয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। সময়ের উল্টো দিকে যেহেতু যাওয়া যায় না, অতএব, যারা অন্যায় করেছিল, তাদের উত্তরসূরিদেরই প্রায়শ্চিত্তের দায় নিতে হবে। এই প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন হয় না।
কোনো ঘটনার আকস্মিকতায় কারও যদি পা পিছলেও যায়, সে যাতে সামলে নিতে পারে, একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকতে না হয় তাকে, তা নিশ্চিত করার দায় রাষ্ট্রের। স্বাধীন বাংলাদেশ সেই দায় নেয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল। বঞ্চিত পিছিয়ে পড়াদের সামনের কাতারে আনার একটা চেষ্টা ছিল। দেশের প্রতিটি শিশু যাতে উন্নতির সমান সুযোগ পায়, সবার যেন শিক্ষার সমান অধিকার থাকে, সমান পুষ্টি জোটে, তা নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। কথাটাকে ভেঙে দেখলে পিছিয়ে পড়াদের পাশাপাশি অন্যদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বের জায়গাটা স্পষ্ট হতে পারে। ধরা যাক, একটি পাঁচিল-ঘেরা জমির মধ্যে একটা বাড়ি, সেই বাড়িতে সমৃদ্ধি থাকে, উন্নয়ন থাকে। কিছু লোক আছে পাঁচিলের ভেতরে, কিছু লোক পাঁচিলেরও বাইরে। সংরক্ষণ হলো পাঁচিলের গেটটুকু খোলা, যাতে বাইরের লোকরাও ভেতরে আসতে পারে। এর পর বাড়ির দরজা-জানালা খোলার কাজ। স্বাধীনতা-উত্তর দেশের নীতিনির্ধারকরা আশা করেছিলেন, রাষ্ট্র সবার জন্য সে দরজাগুলো খুলবে। একটা কথা স্পষ্ট- সুযোগের সাম্য তৈরি করতে চাইলে সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের জোরদার উপস্থিতি প্রয়োজন, সেই জায়গাটি সাধারণ নীতি দিয়ে করা যায় না।
যদিও সংরক্ষণ সব অসাম্য ও পিছিয়ে পড়াদের এগিয়ে নেবার মহৌষধ নয়; কিন্তু সবার জন্য সক্ষমতা ও সাম্য তৈরির পথ খুঁজে বের করার জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন। যত দিন সমাজের একটি শ্রেণি বৈষম্যের শিকার থেকে যাবে, তত দিন সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু রাখার প্রয়োজন রয়েছে। সমাজে যারা দীর্ঘ সময় ধরে বঞ্চনা ও বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে এসেছেন, তাদের জন্য অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন অনিবার্য। সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকে বাদ দিয়ে কোনোভাবেই দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়।
মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দ কোটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা হচ্ছে। শহীদসন্তান ও তাদের পরিবারগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দ ৩০ শতাংশ কোটাকে যৌক্তিক বলেই মনে করছেন। তাদের মতে, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন, তারা মুক্তিযোদ্ধা কোটার বাস্তবায়ন করেননি। এই দীর্ঘ ২১ বছরে বঞ্চিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স শেষ হওয়ার কারণে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে মুক্তিযোদ্ধা কোটার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য মুক্তিযোদ্ধার সন্তান পর্যন্ত এই কোটাসুবিধা বর্ধিত করেন; কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের তখন আর চাকরির বয়স ছিল না। তাই তাদের সন্তানদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।
দেখা গেছে তাদের সন্তানরাও অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। পরে তাই মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-নাতনিদের কোটা সুবিধার আওতায় আনা হয়। ২০০১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ৯ বছর বিএনপি-জামায়াত ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের কোটাসুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। স্বাধীনতার পর মোট ৩০ বছর বঞ্চিত হওয়া মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে তাদের কোটাসুবিধা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটার এখনো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ এখনো হাজার হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বেকার অবস্থায় আছেন।
বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম কোটাসুবিধা দেয়া হয়ে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। মাতৃভূমির প্রতি তাদের প্রেম, দায়বোধ, সাহসিকতা ও অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন এ রাষ্ট্র। তাদের কারণেই আজ আমরা স্বাধীনভাবে চলার ও বলার অধিকার লাভ করেছি এবং এদেশের মাটি-জলে নিজেদের বিকশিত করার সুযোগ পাচ্ছি। এমনকি চাকরি করারও সুযোগ পাচ্ছি। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এ রাষ্ট্রের একটা বিশেষ দায় আছে। মুক্তিযোদ্ধা কোটা সেই দায় শোধেরই একটা চেষ্টা মাত্র। আমরা কি সেই দায় অস্বীকার করে বসব?
চিররঞ্জন সরকার: কলামিস্ট


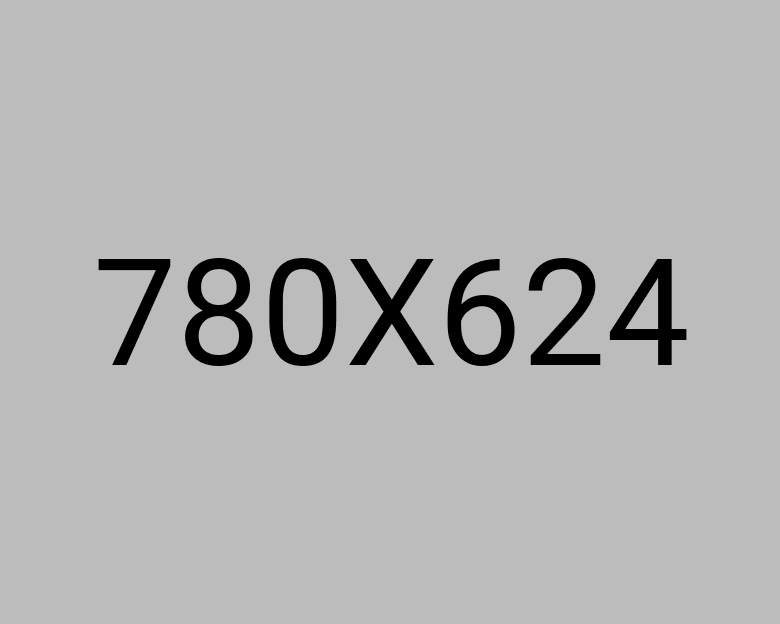
মতামত দিন
মন্তব্য করতে প্রথমে আপনাকে লগইন করতে হবে