সিডরের স্মৃতি: ডাইন পাশ দিয়া যান, বাম পাশে গণকবর

বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ইতিহাসে ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর একটি ভয়াল দিন হিসেবেই চিহ্নিত। এদিন দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে সুপার সাইক্লোন ‘সিডর’। এই ঝড়ে ঠিক কত মানুষ মারা গেছেন, তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। কেননা সরকারি হিসাবের সঙ্গে বেসরকারি হিসাবে তফাৎ অনেক। সরকারি হিসাবে ৩ হাজার ৪০০ মানুষের মৃত্যুর কথা বলা হলেও ওই সময়ে বিভিন্ন বেসরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা বলা হয় প্রায় ১০ হাজার। সিডরের আঘাতে প্রায় ৫৫ হাজার মানুষ আহত ও অনেকেই নিখোঁজ হন। সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হন ৭০ লাখ এবং কয়েক লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েন। উপকূলীয় অঞ্চলের ঘরবাড়ি, কৃষিজমি, গবাদিপশু এবং মাছের খামার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুন্দরবনের অনেক গাছপালা এবং বন্যপ্রাণীও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
সিডর আঘাত হানার পরদিন থেকে প্রায় তিন সপ্তাহ উপকূলের নানা এলাকায় সংবাদ কাভার করার অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, সিডর আসলে উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। ধান, রবিশস্য, গাছ, মাছ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি মিলিয়ে ঠিক কত টাকার ক্ষতি হয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে তা নিরূপণ করা যায়নি। তবে ঘটনার ১৫ দিন পরে ৩০ নভেম্বর সরকারের তরফে যে হিসাব দেয়া হয়, সেখানে বলা হয়, ১২ লাখ ৭৫ হাজার ৩১৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই সময়ে জমিতে ছিল আমন, ইরি ও স্থানীয়ভাবে নাম দেয়া আরও কিছু ধান। তবে ইরি বা উফশী জাতের ধানের চেয়ে আমন ও দেশি অন্যান্য ধানের ক্ষতি কম চোখে পড়ে। স্থানীয় কৃষক এর কারণ হিসেবে স্থানীয় ধানের গোড়া তুলনামূলকভাবে শক্ত বলে জানান।
সিডরের তাণ্ডবে উপকূল অঞ্চলে ক্ষতি হয়েছে দুভাবে। প্রথমত, জলোচ্ছ্বাস ভাসিয়ে নিয়ে গেছে অগণিত মানুষ, পশু-পাখি, বসতি। দ্বিতীয়ত, ২৫০ কিলোমিটার বেগের ঘূর্ণি-হাওয়া উপড়ে ফেলেছে লাখ লাখ গাছপালা। গাছ উপড়ে পড়েছে ঘরের চালায়। ফলে দেখা গেছে, যত লোকের প্রাণহানি ঘটেছে, তার বড় অংশের মৃত্যু হয়েছে ঘরচাপা পড়ে। যেসব গাছ ভেঙে পড়ে, তার মধ্যে বেশি চোখে পড়ে রেইনট্রি, চাম্বল, মেহগনি, শিলকড়াই ও অ্যাকাশিয়া। অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশি বিভিন্ন ফলের গাছ যেমন আম, জাম, আমলকি, ডেউয়া ইত্যাদি। কোনো ক্ষতি হয়নি বলা চলে তাল, নারিকেল, সুপারি ও খেজুর গাছের। হাতে গোনা কিছু সুপারি গাছ পড়ে গেলেও তা অন্য কোনো বড় গাছের আঘাতে পড়ে গেছে।
স্থানীয় প্রবীণরা বলেছেন, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় বায়ুর বেগ ও পানির স্রোত প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে নারিকেল ও সুপারি গাছ। এ ছাড়া ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী সময়ে নারিকেলের পানি ও শ্বাস পানীয় জল ও খাদ্যের বিকল্প হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া শক্ত ও মোটা শিকড় থাকায় তেঁতুল, বট, অশ্বত্থ, বকুল, জারুল, নিম, গাব, জাম, অর্জুন ইত্যাদি গাছ ঘূর্ণিঝড়ের সময় সহজে উপড়ে যায় না। জলোচ্ছ্বাসের সময় ভেলা হিসেবে কাজে লাগে কলাগাছ। ফলে তখন প্রশ্ন ওঠে, উপকূলে যে ধরনের গাছ বেশি থাকা দরকার, তা ছিল কি-না এবং সিডরের মতো ব্যাপকবিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের ১৭ বছর পরেও উপকূলে গাছপালা লাগানোর ক্ষেত্রে সরকারের নীতি এবং স্থানীয়দের মানসিকতায় খুব বড় কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না।
উপকূলের পরিবেশ-প্রতিবেশ নিয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠান কোস্টের গবেষণা অনুযায়ী, ৫০ বছরে বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে চিংড়ি প্রকল্পের দাপটে প্রায় ২২ হাজার একর আয়তনের চকরিয়া সুন্দরবন সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলা হয়- যেটি ছিল দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মানবসৃষ্ট এ কারণ ছাড়াও ম্যানগ্রোভ ধ্বংসের জন্য বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন তথা উষ্ণতা বৃদ্ধিও আরেকটি বড় কারণ। কারণ ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বেড়ে যাচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা, এতে করে উপকূলীয় অঞ্চলের নিম্নভূমি ও উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহের প্লাবিত হওয়া এবং ম্যানগ্রোভ ও জলাভূমির প্রতিবেশ ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে গেছে। আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে যে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন চলছে, সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সুরক্ষার জন্য নানাবিধ সুপারিশ তুলে ধরেছেন।
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এই সম্মেলনে তিনটি শূন্যের নতুন পৃথিবী গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এগুলো হচ্ছে শূন্য কার্বন নিঃসরণ, সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে শূন্য সম্পদ কেন্দ্রীভবন এবং নিজেকে উদ্যোক্তা বানিয়ে শূন্য বেকারত্ব। তার ভাষায়, এভাবে গড়ে উঠবে নতুন সভ্যতা। ড. ইউনূস বলেন, পৃথিবীর মানুষ এমন এক জীবনধারা বেছে নিয়েছে, যা পরিবেশের বিরুদ্ধে কাজ করে; কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে একটি নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে হবে। একটি পাল্টা সংস্কৃতি, যা ভিন্ন জীবনধারার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। কোনো জীবাশ্ম জ্বালানি থাকবে না। শুধু নবায়নযোগ্য জ্বালানিই হবে পৃথিবীর চালিকাশক্তি। সবাই একসঙ্গে স্বপ্ন দেখলে এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব বলে মনে করেন প্রধান উপদেষ্টা। অস্বীকার করা যাবে না, ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা তথা এর সঙ্গে টিকে থাকার বিষয়ে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। ২০০৭ সালে সিডরে যে পরিমাণ মানুষের প্রাণহানি হয়েছে, এর দুই বছরের মাথায় আঘাত হানা আইলায় সেই তুলনায় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল অনেক কম। কেননা সিডরে প্রাণহানির একটি বড় কারণ রাখাল বালকের বাঘের ভয় দেখানো।
উপকূলের মানুষের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে, তাদের অনেকেই এটা বিশ্বাস করতে পারেননি যে ঝড়টি এত বিধ্বংসী হবে। কেননা এরকম সতর্ক সংকেত তারা এর আগেও অনেকবার পেয়েছেন; কিন্তু ঝড় সেভাবে আসেনি। সিডরকে তারা বিশ্বাস করেননি অথবা অতি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। আরেকটি কারণ হলো রেডক্রিসেন্টের স্বেচ্ছাসেবকরা ঝূঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্র তথা সাইক্লোন শেল্টারে যাওয়ার জন্য তাগিদ দিলেও অনেকেই তা আমলে নেননি। কারণ তারা নিজেদের ঘর ও গবাদি পশু অরক্ষিত রেখে যেতে চাননি। অনেকেই গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগির মায়ায় ঝড়ের রাতেও ঘরে অপেক্ষা করেছেন; কিন্তু ঝড় আঘাত হানার পরদিন উপকূলের খালে ও নদীতে দেখা গেছে শত শত গরু মহিষ ভেসে যাচ্ছে।
সিডরের এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা উপকূলের মানুষের মনোজগতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনে। যে কারণে আইলার সতর্ক সংকেত শোনার পরে ঝুঁকিপূর্ণ অধিকাংশ মানুষই সাইক্লোন শেল্টার বা অন্য কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছেন। তাতে প্রাণহানি অনেক কম হয়েছে। বস্তুত এরপরে নার্গিস, বুলবুল, মহাসেন, রিমালসহ আরও যত ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে, তাতে অন্তত প্রাণহানি অনেক কম হয়েছে। অর্থাৎ সিডর ছিল এমন একটি ঘটনা- যা ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাপারে বাংলাদেশের মানুষের চিন্তায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনে। সিডরে ক্ষতি বাড়ার একটি বড় কারণ ছিল আশ্রয় কেন্দ্রের স্বল্পতা। বরগুনার পাথরঘাটার পদ্মা গ্রামের মানুষ জানান, তারা যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, সিডর আঘাত হানছে, তখন আর সময় ছিল না। কারণ যাদের বাড়ি-ঘর আশ্রয়কেন্দ্রের খুব কাছাকাছি তারাই কেবল সেখানে যেতে পেরেছেন; কিন্তু যাদের বাড়ি আশ্রয় কেন্দ্র থেকে দূরে, তারা ঠাঁই নিয়েছেন বেড়িবাঁধ বা উঁচু রাস্তায়। একই তথ্য জানা গেছে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় দুর্গত এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে। সেখানেও প্রয়োজনের তুলনায় আশ্রয় কেন্দ্র অপ্রতুল এবং অনেক আশ্রয় কেন্দ্রের অবস্থা খুবই জরাজীর্ণ। ফলে সেখানে আশ্রয় নেয়া মানুষও এক রকম আশ্রয়হীনতায় ভোগেন।
ভালো সংবাদ হলো, সিডরের পরে উপকূলে ব্যাপক আকারে সাইক্লোন শেল্টার তৈরি করা হয়। অনেক স্কুল ও ইউনিয়ন পরিষদের ভবনও নির্মাণ করা হয় এমনভাবে যাতে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সময় মানুষ এগুলো আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। তার মানে সিডর রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রেও বড় ধরনের পরিবর্তন আনে; কিন্তু বিপরীত চিত্র হলো উপকূলে যে পরিমাণ গাছপালা ও বনভূমি থাকার কথা তা তো নেই, বরং নির্বিচারে গাছপালা কাটা হয়েছে। বন উজাড় করা হয়েছে। আবার বনায়নের নামে নানারকম হাস্যকর কাজ হয়েছে। জনগণের অর্থ লোপাট হয়েছে। প্রয়োজনীয় স্থানে বেড়িবাঁধ না থাকাও সিডরে ক্ষতি বাড়িয়েছে। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের ওপর ‘দ্য বাংলাদেশ সাইক্লোন অব ১৯৯১: হোয়াই সো মেনি পিপল ডায়েড’ শীর্ষক একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, শুধু কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় ঝড়ে নিহত মানুষের সংখ্যা ছিল ১৯ হাজার ১৩৩। তাদের অধিকাংশই ছিলেন নারী ও শিশু। ওই ঝড়ে এত ক্ষয়ক্ষতির অন্যতম কারণ ছিল প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত বেড়িবাঁধ না থাকা।
সিডরেও সেই একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে উপকূলের মানুষ। বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলা শহর থেকে দক্ষিণে বিষখালী ও বলেশ্বর নদীর মোহনা-সংলগ্ন নাম পদ্মা এলাকায় একটি বেড়িবাঁধ রয়েছে; কিন্তু বাঁধের বাইরে থাকা ঘরগুলো সিডরের তাণ্ডবে লন্ডভণ্ড হয়ে গেলেও বেড়িবাঁধ বাঁচাতে পারেনি বাঁধের ভেতরের মানুষগুলোকেও। কারণ বাঁধের একটা বড় অংশ ভেঙে গিয়েছিল বছর কয়েক আগে। সেটি কার্যকরভাবে মেরামত করা হয়নি। সিডরের ১৭ বছর পরেও উপকূলের বিভিন্ন এলাকার দিকে তাকালে একই চিত্র দেখা যাবে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড় আইলায় ২০০৯ সালে খুলনা ও সাতক্ষীরা উপকূলের ৭৬ কিলোমিটার বাঁধ পুরোপুরি এবং ৩৬২ কিলোমিটার বাঁধ আংশিকভাবে ধসে পড়ে। এর বাইরে প্রতি বছর বিভিন্ন এলাকায় বাঁধ ভাঙার খবর পাওয়া যায়। পরে প্রকল্প নিয়ে স্থায়ীভাবে বাঁধ মেরামত করে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো); কিন্তু কিছুদিন পর আবার বাঁধ ধসে প্লাবিত হয় গ্রামের পর গ্রাম।
২০২০ সালের আম্ফানে খুলনার কয়রা উপজেলায় মোট ১১৯ কিলোমিটার বেড়িবাঁধের মধ্যে সাড়ে ৪ কিলোমিটার পুরোপুরি ভেঙে যায়। ৩৩ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ আংশিক ভেঙে গেছে। খুলনার কয়রা উপজেলার ৪৭ গ্রামের দেড় লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েন। গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছাশ্রমে বেড়িবাঁধ মেরামত করেছেন। এ ছাড়া দাকোপ, পাইকগাছা, বটিয়াঘাটা ও ডুমুরিয়া উপজেলায় প্রায় ৮০০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ রয়েছে। এর মধ্যে ৪০-৫০ মিটার পুরোপুরি ভেঙে গেছে। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৪০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ। তিনটি পয়েন্টে সেনাবাহিনী বেড়িবাঁধ মেরামতের কাজ করেছে।
সর্বশেষ গত মে মাসে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় রিমাল আঘাত হানলে তখন নতুন করে সামনে আসে বেড়িবাঁধের প্রসঙ্গটি। তখনো ঝুঁকিপূর্ণ বেড়িবাঁধ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন লাখো মানুষ। অথচ বাঁধ সংস্কারে বছর বছর ব্যয় হয় কোটি কোটি টাকা। দুর্যোগ এলেই বাঁধ নিয়ে শুরু হয় তোড়জোড়। বরাদ্দ হয় টাকা, এর পরও ভেঙে যায় সেই বাঁধ। আবার সেই বাঁধ সংস্কারের নামে চলে শত শত কোটি খরচের নামে লুটপাট। যে কারণে দিন শেষে কোনো সুফল মেলে না। উপকূলীয় এলাকার মানুষেরা রসিকতা করে বলেন, বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য যে টাকা এখন পর্যন্ত খরচ করা হয়েছে বা বরাদ্দ হয়েছে, সেই টাকা বান্ডিল করে ভেঙে যাওয়া বাঁধে ব্লক হিসেবে ব্যবহার করা যেত।
পরিকল্পিত ও স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ না হওয়ায় প্রতি বছর ভাঙন দেখা দেয়। এ জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের গাফিলতিই দায়ী। কারণ যখন জোয়ারের পানি বাঁধ উপচে পড়ার উপক্রম হয়, তখন স্বেচ্ছাশ্রমে বাঁধ মেরামতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এলাকাবাসী। এ সময় বাঁধ মেরামতে উদ্যোগ নেয় কর্তৃপক্ষ। এতে একদিকে কাজের ব্যয় বাড়ে, অন্যদিকে এসব কাজ হাত ঘুরে নিম্নমানের হয়। আবার ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধের তালিকা করে বরাদ্দের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠালেও তা অনুমোদন হতে সময় লাগে। ফলে কোথাও ভাঙনের শঙ্কা দেখা দিলে সেখানে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া যায় না। স্থানীয় মানুষ নিজেদের প্রচেষ্টায় যেভাবে পরে বাঁধ রক্ষার চেষ্টা করে।
স্থানীয় দ্বন্দ্বের কারণেও অনেক সময় বেড়িবাঁধের ভাঙা অংশ দ্রুত মেরামত করা যায় না। এতে বাঁধের ফাটা অংশ আরও বড় হয়। মূলত বাঁধের ভাঙা অংশ মেরামতের জন্য বালু সরবরাহ নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। বাঁধের ভাঙা অংশের পেছনে রিং বাঁধ নির্মাণের জায়গা নিয়েও সমস্যা দেখা দেয়। স্থানীয় মানুষজন স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ওই বাঁধ মেরামত করেন; কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ডের দায়িত্ব থাকে বাঁধের দুই পাশে বালুর বস্তা ও বালুর টিউব দিয়ে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা; কিন্তু বালু ও শ্রমিক সরবরাহ নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, ঠিকাদার ও প্রভাবশালীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ফলে কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে বাঁধের কাজ শেষ করার পর তা আবার ভেঙে যায়। বাঁধ নির্মাণ-সংস্কার-মেরামতের ঠিকাদারদের অধিকাংশই স্থানীয় নন। ফলে যে ঠিকাদার কাজ পান, তিনি বিক্রি করে দেন আরেক ঠিকাদারের কাছে। তার কাছ থেকে কাজ নেয় আরেকজন। এভাবে ঠিকাদার বাঁধের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ পর্যায়ক্রমে কমতে থাকে। কাঙ্ক্ষিত কাজটি হয় না।
অর্থাৎ প্রতি বছর বাঁধ সংস্কারে বরাদ্দ এলেও নানা হাত ঘুরে সেই কাজটি আর ঠিকমতো হয় না বলে সারা বছরই টেকসই বাঁধের জন্য মানুষকে চিৎকার করতে হয়। সুতরাং, ১৭ বছর আগের সিডর, তারপরে আইলা ও অন্যান্য ঘূর্ণিঝড়ের স্মৃতি মনে রেখে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সাজানো দরকার। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতি বছর উপকূলে নদীভাঙন, জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় থেকে ক্ষতি কমাতে বড় পরিকল্পনা দরকার। সেইসঙ্গে বাঁধের সংরক্ষণ-সংস্কার-মেরামতের কাজ ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদসহ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে করার দাবিও দীর্ঘদিনের। এখানে পানি উন্নয়ন বোর্ড কেবল কারিগরি সহায়তার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় নিয়ে জনগণের অভিজ্ঞতা ও মতামতের ভিত্তিতে কমপক্ষে আগামী একশো বছরের জন্য স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোজন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা দরকার।
সিডরের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে লেখাটি শেষ করা যাক। সিডর আঘাত হানার তৃতীয় বা চতুর্থ দিন সন্ধ্যার পরে বরগুনার স্থানীয় সাংবাদিক সোহেল হাফিজকে সঙ্গে নিয়ে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় যাচ্ছিলাম। মোবাইল ফোনের আলো জ্বেলে আমরা পথ চলছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে হাতের ডান দিকে একটা ছোট্ট দোকানের (ঝড়ে বিধ্বস্ত) সামনে কিছু লোকের জটলা দেখা গেল। তারা আমাদের হাঁটার গতি দেখে সাবধান করে বললেন যে আমরা রাস্তার ডান দিক দিয়ে হাঁটি। কেন? তারা বললেন, সামনেই গণকবর। গণকবর শব্দটা শুনে আমাদের পায়ের গতি থেমে যায়। কিছুটা ভয় পাই। আমি সোহেলের হাত চেপে ধরি। হাঁটার গতি কমাই।
লোকেরা বললেন, সিডরের তাণ্ডবে যে জলোচ্ছ্বাস হয়েছে, তাতে ওই এলাকার অধিকাংশ কবর ও শুকনো জায়গা ডুবে গেছে। মৃতদের দাফন করার মতো জায়গা ছিল না। ফলে উঁচু রাস্তার পাশেই তাদের দাফন করতে হয়েছে। জায়গাটা কিছু ডালপালা দিয়ে ঘেরাও করা; কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে সেটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। বরগুনা সদরের ১০ নম্বর নলটানা ইউনিয়নের গর্জনবুনিয়া গ্রামের এই উঁচু স্থানে ১৯টি কবরে ২৯ জনকে দাফন করা হয়েছে। পরবর্তীতে স্থানীয় প্রশাসন সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে। প্রায় দেড় যুগ আগে একটি জাতীয় দৈনিকের একজন জুনিয়র রিপোর্টার হিসেবে ঢাকা থেকে গিয়েছিলাম ওই ভয়াল দুর্যোগের সংবাদ কাভার করতে। এতদিন পরেও কানে বাজে সেই কথা: ‘ডাইন পাশ দিয়া যান, বাম পাশে গণকবর।’
আমীন আল রশীদ: সাংবাদিক ও লেখক।


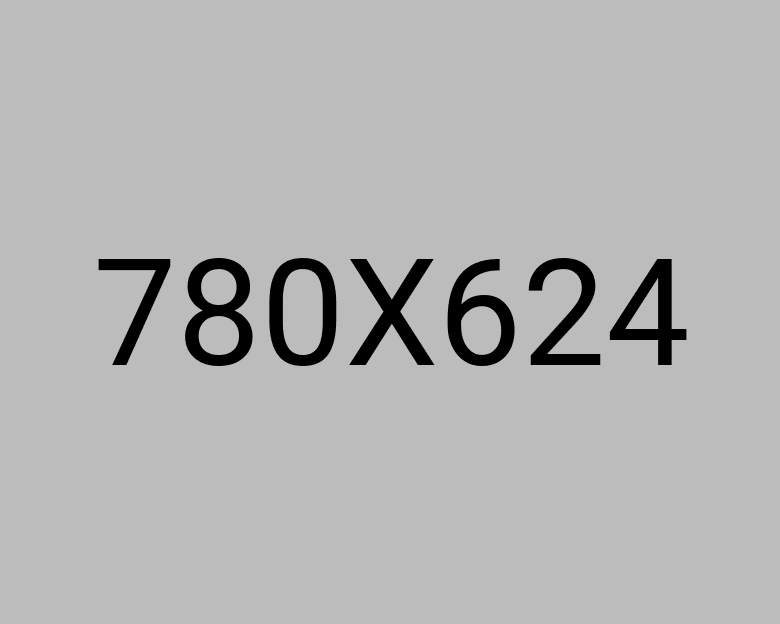
মতামত দিন
মন্তব্য করতে প্রথমে আপনাকে লগইন করতে হবে